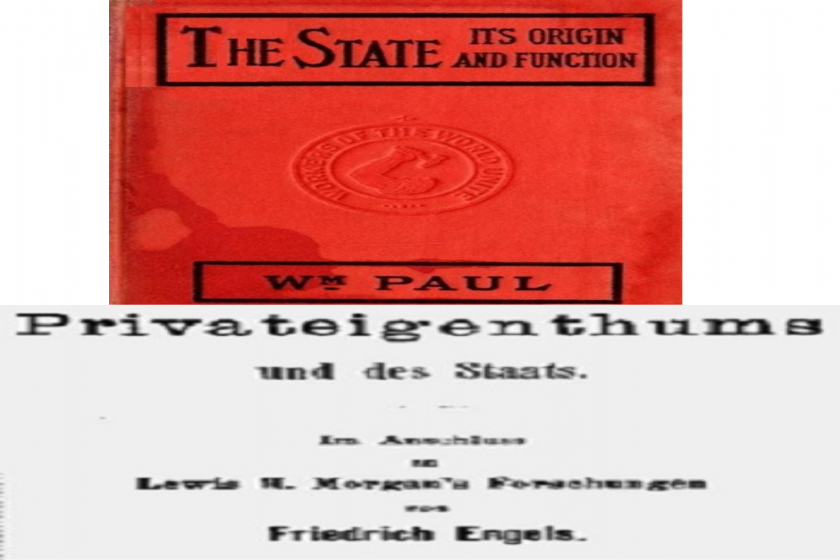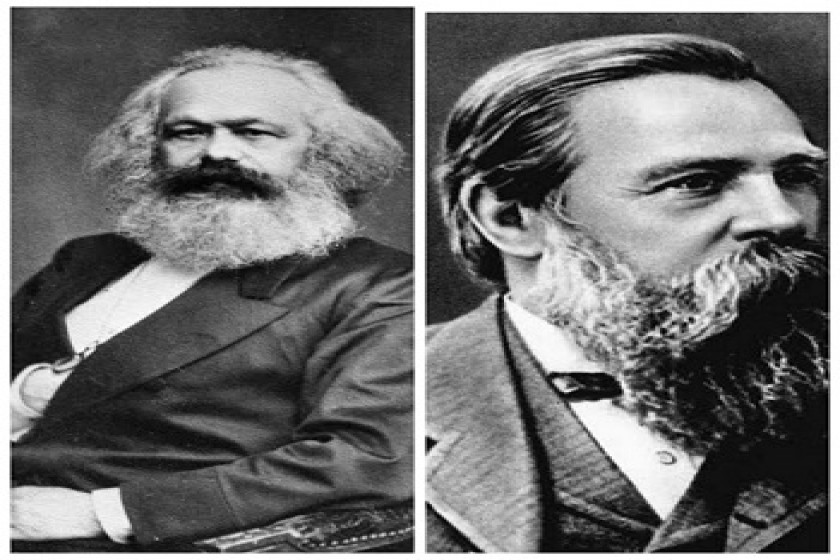বিশ্বাসের বিজ্ঞান: বিশ্বাস বনাম যুক্তিতথ্য
অশোক মুখোপাধ্যায়
উত্তর ভারতের লাল শালু পরা,সম্প্রতি জ্ঞানপীঠ পুরস্কার (২০২৪) প্রাপ্ত, সেই আধ্যাত্মিক গুরু ও কবি রামভদ্রাচার্যকে ধরেই এবারের কথকতা শুরু করা যাক।
সঙ্ঘ পরিবার ও বিজেপি সরকারের তরফে অযোধ্যায় আইনি পথে লুটে পাওয়া বাবরি মসজিদের জমিতে এক মেগাস্টাইল রাম মন্দির স্থাপন শেষে তার দ্বারোদ্ঘাটন কালে অনেকেই যখন ইতিউতি মন্তব্য করছিলেন যে দেশের এখন মন্দির নয়, হাসপাতাল দরকার, এই আধ্যাত্মিক গুরু বাবাজীবন তার একটা জবাব দিয়েছিলেন, “রাম মন্দির কি স্থাপনা হো জানে সে অস্পাতাল কি কোই জরুরত হি নহি পড়েগি।” ভাবখানা ছিল, স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্রের এই বিরাট মন্দিরে অধিষ্ঠান হয়ে গেলে এবং দেশের সুভক্ত পিএম-এর হাতে তার দ্বারোদ্ঘাটন সুসম্পন্ন হতে পারলে তার ছটায় দেশের সমস্ত রোগভোগ কোথায় চলে যাবে। ভক্তদের আর কখনও অসুখ বিসুখ করবে না।
সত্যিই এমনটা হলে মন্দ ছিল না। কিন্তু গুরুবাবার কপাল ভয়ঙ্কর খারাপ। রামচন্দ্র নিজে বা স্বয়ং বিষ্ণু বোধ হয় তার উপর কোটি কোটি লোকের “স্বাস্থ্যসাথী”প্রকল্পেরএরকম ভারি দায়ভার চাপানো এক দম পছন্দ করেনি। হাজার হোক, বড় বড় কর্পোরেট হাসপাতালগুলির মালিকদের অনেকেও তো আবার রাম ভক্ত। তাদের মুখের খাবারই বা রাম কীভাবে কেড়ে নেবে! কৃতজ্ঞতা এবং চক্ষুলজ্জারও তো একটা ব্যাপার আছে। ফলে হল কী, মন্দির দ্বারোদ্ঘাটনের সাত দিনের মধ্যে রামভদ্র পড়ে গেল মারাত্মক বিমারিতে। তাকে নিয়ে যেতে হল এক নামি এবং দামি হাসপাতালে। বাস্তবে দেখা গেল, “বিশ্বাসে মিলায় খাজা তর্কে তবু কিছু!”
[১] বিশ্বাসের রকমফের
এই বিশ্বাসের প্রশ্নটিকেই বর্তমান প্রবন্ধে একটু চুলচেরা বিচার করে দেখে নিই।
অনেকে মনে করেন, ধর্মেই শুধু বিশ্বাসের কথা আছে, বিজ্ঞানের জগতে বিশ্বাসের কোনো স্থান নেই। বিজ্ঞানীরা এবং বিজ্ঞানপন্থীরা নিজের ব্যবস্থাপনায় যাচাই না করে কোনো কিছুই গ্রহণ করেন না।
কথাটা সত্য নয়। গণ বিজ্ঞান আন্দোলন শিবিরের একজন সামান্য কলমচি হিসাবে আমি বলতে পারি, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বিশ্বাসের ব্যাপক উন্মুক্ত ক্ষেত্র পড়ে আছে। আমরা বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস করি। বিজ্ঞানীদের লেখাপত্রকে বিশ্বাস করে মেনে নিই। মাক্স প্লাঙ্কের e = hν, আইনস্টাইনের e = mc2 সূত্রগুলির পশ্চাদ গণনা না দেখেই আমরা ধরে নিই, অঙ্কগুলি শুদ্ধ। লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডে জিঙ্কের ছিবড়ে ফেললে পাত্রে জিঙ্ক সালফেট উৎপন্ন হবে আর হাইড্রোজেন গ্যাস বেরিয়ে যাবে—এও আমরা হাতে কলমে পরীক্ষা না করেও বিশ্বাস করি। আমরা যে কোনো পরীক্ষার ব্যবস্থা করে সেই সব নিয়ম বা সূত্রের শুদ্ধতা আগে নিজেরা যাচাই করে নিই, তার পর সেই সবকে সত্য বলে মেনে নিই, এমনটাও নয়। আমরা এই সূত্রগুলির সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করেছি।
আবার ধর্মের মঞ্চেও বিশ্বাসের কারবার আছে। বেশ ভালো রকম। ধার্মিক লোকেরা আত্মায় পরমাত্মায় বিশ্বাস করে, ভগবানে (এবং ধর্ম ভেদে তার বিভিন্ন নামে, আল্লায়, গডে, যিহোভায়) বিশ্বাস করে, মুসা যিশু রাম কৃষ্ণের বাস্তব জাগতিক অস্তিত্বে বিশ্বাস নিয়ে চলে, অসংখ্য দেব দেবীতে বিশ্বাস করে, সেই সব দেবতার নানা রকম মাহাত্ম্যে এবং/অথবা তাদের এবং ধর্মগুরুদের বিবিধ প্রকার অলৌকিক কীর্তিকলাপের কাহিনিতে বিশ্বাস করে থাকে, এমনই আরও কত কিছুতে যেতারা বিশ্বাস স্থাপন করে রাখে, তার ইয়ত্তা নেই।
তাই যদি হয়, সতর্ক পাঠক নিশ্চয়ই এখানে জিগ্যেস করতে পারেন, আমি এই প্রবন্ধের শিরোনামে দ্বিতীয় ভাগে তাহলে যুক্তি তথ্য আর বিশ্বাসের মাঝখানে একটা “বনাম” বসালাম কেন? ধর্মীয় বিশ্বাস বনাম বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস—এরকম লিখলাম না কেন?
সেটাই এই লেখার রহস্য। তবে শুরুতেই সেটা বুঝিয়ে বলতে চাই।
প্রথমেই দেখাতে চাইছি,বিশ্বাসেরও রকমফের আছে। গোদা অর্থে বিশ্বাস দুরকমের হয়।
একটা হচ্ছে ব্যক্তি নিরপেক্ষ যাচাই নির্ভর এবং যাচাই সাপেক্ষে বিশ্বাস। যাচাই আবার নৈর্ব্যক্তিক যুক্তি তথ্য তর্ক পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ নির্ভর। তার ভিত্তিতে বিশ্বাস। আমি নিজে হয়ত এখনও যাচাই করিনি। যাচাই না করেই বিশ্বাস করছি। কিন্তু চাইলে, বা সন্দেহ হলে, আমি যেকোনো সময় যাচাই করে নিতে পারি। কীভাবে তার সত্যতা যাচাই হবে তারও উপায় এবং প্রকরণ আমার সম্পূর্ণ জানা আছে। প্রতিটি প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং/অথবা পদক্ষেপগুলি আমি জানি। যে সূত্রে আমি একটা জিনিস জেনেছি, সেই সূত্রকে আমার বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে। আবার আমি সামান্য সন্দেহ হলেই বা কেউ চ্যালেঞ্জ করলেই সূত্রটিকে যাচাইও করে নিতে পারি।
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেটা কাজ করে তা এই ধরনের বিশ্বাস, তবে বেশ বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য বিশ্বাস।
ধর্মীয় বিশ্বাসের চরিত্র একেবারেই আলাদা। প্রথমত সেখানে যাচাইয়ের কোনো প্রশ্ন তো নেইই, সুযোগও নেই। যুক্তি তর্ক খানিক হয়ত আছে। কিন্তু সেও নিতান্তই ব্যক্তি সাপেক্ষ আলোচনা। শঙ্করাচার্য ব্যাসকে মেনেছেন। আমি আচার্য শঙ্করকে মেনে নিয়েছি। গুরুকে, শাস্ত্রকে না মানলে, সংশয় বাচক তর্ক তুললে এক কালে তো সারা পৃথিবীতেই ভয়ঙ্কর বিপদ ছিল। প্রাণ সংশয় হতে পারত। নিদেন পক্ষে বাস্তিলবাস ধার্য হতই। সার্ভেতাস বা ব্রুনোর কথা আমরা তো ভুলে যাইনি। কিংবা গ্যালিলেওর গৃহবন্দি জীবনের কথা। আর ভারতে? সেই কত কাল আগে বৃহদারণ্যক উপনিষদে লেখা হয়েছিল, বারংবার প্রশ্ন তোলায় বিদুষী গার্গীকে যাজ্ঞবল্ক্য হুমকি শুনিয়েছিল, দেবতাদের বিষয়ে অতিরিক্ত প্রশ্ন কোরো না কন্যা, করলে তোমার মুন্ডু খসে পড়বে। তা, ঘটনাচক্রে মুন্ডু তো আর কারও নিজে নিজে খসে পড়ে না, কেউ খসিয়ে না দিলে।
হ্যাঁ, ঠিকই, এগুলো তো আর সত্য ঘটনা নয়, রূপক কাহিনি মাত্র। উপনিষদ তো আর কোনো ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি নয় যে সেখানে যা কিছু আছে তাকে তথ্য বা বাস্তব ঘটনা বলে মেনে নিতে হবে। আমিও বলব, না, সেভাবে মানা যায় না।
কিন্তু তাতেও দুটো কথা আছে।
প্রথমত, আজকের পরিবেশে যখন মহাকাব্যের বর্ণিত পাত্র রামকে ঐতিহাসিক চরিত্র হিসাবে দেখানো হচ্ছে, তার জন্মস্থান খোঁজা হচ্ছে, সেখানে তার নামে জমি বরাদ্দ হচ্ছে এবং আইন আদালতে তা সিদ্ধও হচ্ছে, সেখানে—আমাদের মতো বস্তুবাদী যুক্তিবাদীদের মতামত যাই হোক, তাদের কাছে একই যুক্তিতে যাজ্ঞবল্ক্য এবং গার্গীকেও বাস্তব চরিত্র এবং বর্ণিত আখ্যানকে সত্য ঘটনা বলে ধরে নেওয়ার কথা। দুই জায়গায় তো আর দুরকম যুক্তির খেল দেখানো উচিত নয়। আমার যেখানে সুবিধা, সেখানে সাহিত্যের নায়ককে ইতিহাসের চরিত্র বলে ধরে নেব, আর যেখানে অসুবিধা সেখানে সাহিত্য বর্ণিত পাত্রপাত্রীকে কল্পনা বলে চালাতে চাইব—এরকম হলে তো চলে না।
দ্বিতীয়ত, তথাপি, তর্কের খাতিরে এবং আমাদের বিজ্ঞানমনস্ক অবস্থানের সাপেক্ষে না হয় আপাতত মেনে নিচ্ছি, এগুলো সবই রূপক কাহিনি। কল্পকথা। বাস্তব কোনো ঘটনার যথাযথ বিবরণ নয়। বটেই তো! কিন্তু তাতেই বা কী? এগুলো কী ধরনের ঘটনার রূপক? একটা বেশ উচ্চমার্গীয় উপনিষদে এরকম একটা রূপক কাহিনি নির্মাণের প্রয়োজন পড়ল কেন? এর উলটো ধরনের কোনো রূপক কাহিনি সেই উপনিষদে বা অন্যত্র নির্মিত হল না কেন? এই জাতীয় প্রশ্নগুলোকেও তো এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।
যেভাবেই দেখি, ধর্মীয় চিন্তায় বিশ্বাসের ভূমিকাটা অনপেক্ষ। যুক্তি তথ্য তর্কের মাধ্যমে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে যাচাই সাপেক্ষ বিশ্বাসের মতো নয়। বিশ্বাস এখানে আরও কিছু পূর্বতন বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেগুলো আবার আরও পেছনকার বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে। বিশ্বাস থেকে শুরু, বিশ্বাসেই শেষ। কোনো পর্যায়েই আপনি আধ্যাত্মিক মার্গের বিশ্বাসের পেছনে কোনো যাচাই যোগ্য যুক্তি তর্ক ও তথ্য দেখতে পাবেন না।
যেমন আচার্য রামভদ্রের বিশ্বাসের কথাই ধরুন। রামের মন্দির স্থাপিত হয়ে গেলে, মন্দিরে রামের প্রাণ অধিষ্ঠিত হয়ে গেলে, আর কোনো হাসপাতালের প্রয়োজনই থাকবে না, এই বিশ্বাস তিনি কোত্থেকে পেলেন? ভগবানে বিশ্বাস থেকে, ভগবানের ভক্তের প্রতি অশেষ কৃপায় বিশ্বাসের জোর থেকে, “ভক্তের বোঝা ভগবান বয়”, “শরীর দিয়েছেন যিনি রক্ষাও করবেন তিনি”—এই জাতীয় বহু প্রচলিত আপ্তবাক্য থেকে। এই আপ্তবাক্যগুলির সত্যতা কখনও কোনো ভক্ত পরীক্ষা করে দেখার কথাও ভাবে না। রামকৃষ্ণের কেন কর্কট রোগ হয়েছিল, বিবেকানন্দ কেন অত কম বয়সেই রোগে ভুগে মারা গেলেন—এই সব তথ্য উপরোক্ত আপ্তবাক্যগুলির পক্ষে যায়, না, বিরুদ্ধে, তাও তারা খতিয়ে দেখতে চায় না।
শুধু হিন্দু ধর্মে নয়, ইহুদি, খ্রিস্টান ইসলাম ধর্মেও নয়। কোনো ধর্মেই কেউ খতিয়ে দেখে না।
না, ভুল হল। শুধু খতিয়ে দেখে না, এমন নয়। তখন তারা এই অসুবিধাজনক তথ্যগুলির রক্ষার্থে এক “লীলা তত্ত্ব” সামনে নিয়ে আসে। এসব হচ্ছে ভগবানের লীলা। সে এইভাবে ভক্তের নাকি পরীক্ষা নেয়। ভক্তের বোঝা বহনের তখন কী হয়—সেই প্রশ্নের উত্তর আর তারা দিতে পারে না বা চায় না। কিংবা, ঈশ্বর কখন কার কাছে যে কী চায়, কে বলতে পারে! একে আজকাল অনেকে বলেন গোলপোস্ট পালটে ফেলা। কথা হচ্ছিল এক জায়গায়, সেখানে অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে দেখে অন্য জায়গায় কথাটাকে নিয়ে যাওয়া। প্রসঙ্গ বা প্রতিপাদ্য বদলে দেওয়া। তর্কশাস্ত্রের নিরিখে এ এক অতি পুরনো কিন্তু খুব দুর্বল পদ্ধতি। অথবা এক প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে একটা প্রতিপ্রশ্ন দাঁড় করানো।
পদ্ধতি যাই হোক, এটা স্পষ্ট যে আধ্যাত্মিক লাইনে এই ধরনের বিশ্বাসের পক্ষে তথ্য ও যুক্তির কোনো জোরদার ভিত্তি স্থাপনের জায়গা নেই।
বিজ্ঞানের যে কোনো সত্যে বা সূত্রে বিশ্বাস স্থাপনের অন্যতম শর্তই হল, পর্যাপ্ত তথ্য ও যুক্তি। আর সেই সবকে ঘিরে প্রশ্ন উঠলে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা। এক প্রশ্ন থেকে ভিন্ন প্রশ্নে যেতে হলে সূত্র পালটে ফেলা হয় না বা যায় না। একই ধরনের তথ্যে একই সূত্র প্রয়োগ করে দেখাতে হয় যে সত্যটা একই রকম ভাবে সর্ব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিপরীত ক্রমে বলা যায়, বিজ্ঞানের একটা সূত্র যত বেশি তথ্যকে ব্যাখ্যা করতে পারে, ততই তার ক্ষমতা।
আসল কথা হল, বিজ্ঞানের বিশ্বাসটা সর্বদাই প্রয়োজন মতো পর্যবেক্ষণ পরীক্ষা ও যাচাই প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রতিস্থাপন যোগ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস সর্বদাই আরও কিছু বিশ্বাসের অবলম্বন ছাড়া দাঁড়াতে পারে না। সম্ভবত এই জন্যই বিজ্ঞানের জ্ঞানে ভুল ধরা পড়ে, ভুলের সংশোধন হয়। ধর্মীয় চিন্তার জগতে ভুলের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত। সুতরাং সেখানে ভুল সংশোধনের কোনো জায়গাই নেই। আইনস্টাইন ভুল বলেছেন, পাভলভের বয়ানে ত্রুটি ছিল, এরকম বললে বিজ্ঞানীদের সভায় বা বিজ্ঞান কর্মীদের মধ্যে কোনো দাঙ্গা হাঙ্গামা হবে না। খুব উচ্চকণ্ঠে হয়ত তক্কাতক্কি হবে। কিন্তু ভক্তদের মধ্যে দাঁড়িয়ে রামের অন্যায় হয়েছিল, মহম্মদ ভুল বলেছেন, বললে দাঙ্গা লেগে যাওয়ার সম্ভাবনার ব্যাপারে ৮৭ শতাংশ গ্যারান্টি দেওয়া যায় (বাকি ১৩ শতাংশ রাখতে হচ্ছে উলটো বিপত্তির ভয়ে; দাঙ্গাকারীও কখনও কখনও ভয় পায়!)। যুক্তি তর্ক তখন বল্লম আর চাপাতির রূপে আত্মপ্রকাশ করে।
[২] প্রসঙ্গ দশাবতার ও বিবর্তন।
একটা উদাহরণ তুলে এনে এই দুই প্রকারের বিশ্বাসের মধ্যে তফাতটা আরও খোলসা করা যাক।
আমাদের দেশের অনেকেই আজকাল মনে করেন, বিষ্ণুপুরাণে যে দশাবতার তত্ত্ব প্রচারিত হয়েছে, তার মধ্যে জীব বিবর্তনের একটা প্রাথমিক অনুমান অন্তত আছে। আধুনিক জীব বিবর্তনের ডারউইনীয় তত্ত্ব যেভাবে বিষয়টাকে উত্থাপন ও ব্যাখ্যা করেছে, একেবারে হুবহু সেরকম না হলেও যেভাবে ভগবানের অবতারের প্রাচীনতর রূপগুলি জলচর মাছ (মৎস্য), তারপর কচ্ছপ (কূর্ম) যে জলে এবং স্থলে থাকতে পারে, পরে পুরোপুরি স্থলচর হিসাবে শুয়র (বরাহ) ইত্যাদি প্রকরণের মধ্য দিয়ে নৃসিংহ অবতারের পর পুরোপুরি নরদেহ ধারণ করেছে রাম কৃষ্ণ পরশুরাম প্রমুখর মধ্যে—এর মধ্যে যেন একটা ক্রম পরিণতির আভাস দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ, নামে দশাবতার তত্ত্ব হলেও এ যেন প্রাচীন হিন্দুদের বিবর্তনের ধারণার বৈজ্ঞানিক উপস্থাপনা। অনেকেরই মনে পড়ে যাবে, এক সময় প্রখ্যাত বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার সঙ্গে বিতর্কে নেমে পুঁদুচ্চেরি আশ্রমের অরবিন্দ শিষ্য অনিল বরন রায় ঠিক এইভাবেই যুক্তি উত্থাপন করেছিলেন।
যাঁরা সত্যিই এই ভাবে বিশ্বাস করেন, তাঁদের ভাবনাচিন্তার ভিত্তি কী?
দুটো জিনিস।
প্রথমত, তাঁরা যখন থেকে ডারউইনের তত্ত্ব জেনেছেন, তখন থেকে তাঁদের একটা অন্যতম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র সমূহ থেকে এমন কিছু নথিসাক্ষ্য খুঁজে বের করা যার মধ্যে প্রাণীজগতের ক্রমপরিবর্তনের একটা ছবির আংশিক হলেও সাদৃশ্য পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণের দশাবতার তত্ত্ব তাঁদের সেই অনুসন্ধিৎসাকে খানিকটা হলেও সন্তুষ্ট করতে পারে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এটাই তাঁদের চিন্তার শুরু, এখানেই সেই চিন্তার অবসান। তাঁরা তাঁদের এই বিশ্বাসকে আর বাজিয়ে দেখতে আগ্রহ বোধ করেন না।
দ্বিতীয়ত, এই দশ অবতার প্রকল্পনার মধ্যে জীব বিবর্তনের ধারণা এমনকি ভ্রূণ আকারে থাকতে হলেও তাকে কী কী প্রাথমিক শর্ত পূরণ করতে হত, তাও তাঁদের চিন্তায় কখনও জায়গা পায় না। অর্থাৎ, বিবর্তনের বৈজ্ঞানিক ধারণার মূল বৈশিষ্ট্য বা আধারটা কী সে সম্পর্কেও তাঁদের কোনো স্পষ্ট আন্দাজ নেই। জীব জগতের বিবর্তন মানে তো শুধু আর ক্রমিক কিছু প্রাণীর আবির্ভাব বোঝায় না, আরও কিছু বোঝায়। সেইগুলো না থাকলে বা দেখাতে না পারলে মাছ কচ্ছপ শুয়র আর মানুষ—এই রকম ক্রমিক আবির্ভূত কয়েকটি প্রাণীর উল্লেখ করলেই তা বিবর্তনের ছবি যে হয়ে ওঠে না, এই বোধটাও তাঁদের হয়নি।
প্রসঙ্গত বলি, এই বিষয়ে মেঘনাদ সাহা সেকালে তাঁর বক্তব্যের সমালোচনা করে অরবিন্দ শিষ্য অনিল বরন রায়ের উত্থাপিত বয়ানের উত্তরে লেখা পূর্বোক্ত প্রবন্ধে সবিস্তারে কিছু দরকারি কথা বলে গেছেন। আগ্রহী পাঠকদের তরফে সেটা আগে একবার দেখে এবং পড়ে নেওয়া যেতে পারে। আমি এখানে তার সঙ্গে আরও কিছু কথা যোগ করতে চাইব, বিষয়টার আরও চূড়ান্ত ফয়সালা করে ফেলার উদ্দেশ্যে:
১) জল আর জীবন যে খুবই অন্বিষ্ট এটা প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ জানত। আদিম কালের মনুষ্য বসতিগুলি অধিকাংশই গড়ে উঠেছিল হ্রদ বা নদী এবং সমুদ্রের ধারে ধারে। এর একটা কারণ পানীয় জলের চাহিদা মেটানো। আর একটা কারণ হল, সেই সব জায়গাতেই সাধারণত বন জঙ্গল একটু পাতলা হত এবং ঝুপড়ি বানিয়ে থাকা সহজ হত। জলের খোঁজে যে প্রাণীরা আসবে তাদের ধরা বা শিকার করাও এতে সুবিধাজনক হয়ে পড়ত। আবার জলের মাছ বা অন্য প্রাণী শিকার করে বা ধরে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করতেও সুবিধা হত। সুতরাং প্রাচীন কালের লোকেরা যখন অবতার কল্পনা করবে, তারও প্রথম আবির্ভাব যে জলেই হতে পারে এটা সেই আদ্যি কালের প্রেক্ষিতে খুব স্বাভাবিক চিন্তা। এর মধ্যে বিবর্তনের চিন্তা জন্ম নেবার কোনো সুযোগই ছিল না। প্রশ্নও ছিল না।
২) তথাপি এর মধ্যে বিবর্তন সংক্রান্ত কোনো ভাবনা সত্যিই কাজ করেছিল কিনা বুঝতে হলে, দেখতে হবে, ক] গাছপালার ব্যাপারে বিষ্ণুপুরাণ কী ভেবেছিল। সেই ক্ষেত্রেও তারা কোন ক্রমিক পর্যায়ে আবির্ভূত উদ্ভিদের কথা ভাবতে পেরেছিল কিনা। এটা না পারার অর্থ হল, জীব জগতের একটা অর্ধাংশকে তারা তাদের বিবর্তনের কথিত “ভ্রূণ মানচিত্র” থেকে বাদ রেখে দিয়েছিল; খ] বিষ্ণুপুরাণ কি অবতারদের কোনো অমেরুদণ্ডী রূপ কল্পনা হয়েছিল?; নাকি প্রথমেই মেরুদণ্ডী প্রাণী থেকে ক্রম পরিবর্তন হয়েছে বলে তারা ভেবেছিল? যদি তাই হয়ে থাকে (আসলে হয়েছেও), তার মানে হল তারা প্রাণীজগতের প্রায় নব্বই শতাংশ সম্পর্কে কোনো ধারণাই সেই কালে কুলিয়ে উঠতে পারেনি। তাহলে, উদ্ভিদ আর প্রাণী মিলিয়ে তারা পঁচানব্বই শতাংশ জীব সম্পর্কেই বিবর্তনের কোনো ছক নির্মাণ করতে বা ভাবতে সক্ষম হয়নি। গ] মাছ থেকে কোনো অব্যবহিত ক্রম দেখা যাচ্ছে না (যেমন,উভচর হিসাবে ব্যাঙ); অর্থাৎ অবতারের অবতরণ বিবর্তনীয় একটা বড় ধাপ লাফ দিয়ে পেরিয়ে এসেছিল। যাঁরা দশাবতারে বিবর্তন দেখেন তাঁরা আবারএই ফাঁক পূরণ করতে কচ্ছপকেই উভচর ভেবে নেন। অর্থাৎ, তাঁদের উভচর প্রাণীর ধারণা হচ্ছে আম আদমির সাধারণ বোধভাস্যি—যে প্রাণী জলেও থাকে স্থলেও থাকতে পারে। অথচ উভচর প্রাণীর বৈজ্ঞানিক ধারণা হল, সে ডিম ফুটে বাচ্চা হওয়ার সময় থেকে কিছু দিন জলে থাকে, তারপর বড় হলে ডাঙায় উঠে আসে। এই ধারণা বিপত্তিও প্রমাণ করে যে বিষ্ণুপুরাণে বিবর্তনের এমনকি কোনো ধারণাভ্রূণও ছিল না; ঘ] সরীসৃপ থেকে স্তন্যপায়ীর দিকে যাওয়ার সময় একটা খুব বড় এবং উল্লেখযোগ্য শাখা হিসাবে পাখির কথা ভাবতেই হয়। পাখি প্রাচীন কাল থেকেই মানুষের কল্পনার জগতকে নানা ভাবে আলোড়িত করেছে। অথচ অবতর তালিকায় কোনো পাখি নেই। কেউ কেউ অবশ্য বলতে পারেন, কেন বিষ্ণুর বাহন হিসাবে গরুড় কল্পনার মধ্যেই তো এই ফাঁক ভরিয়ে দেওয়া হল! হল হয়ত, বিবর্তনের এত বড় একটা কাজের জন্য বাহন একটা না হলে বোধ হয় ঝামেলা হত; ঙ] লক্ষণীয় যে বিষ্ণুর এই প্রাচীন তিন অবতারদের কেউ সেই সময়ের মানুষদের খাদ্য তালিকা বহির্ভূত নয়। এর থেকে সন্দেহ করা যেতেই পারে, নানা রকম কুলকেতুত্ব (totemism)-এর ধারণা ও বিশ্বাস থেকে সেকালের মানুষ যে প্রাণীকুল থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে পেরেছিল, তাদেরকেই এই ভাবে সম্ভবত মহিমান্বিত করে রাখতে চেয়েছিল; ইত্যাদি।
৩) এই ভাবে দেখলে সহজেই বোঝা যাবে, বিষ্ণুর দশ অবতারের প্রকারভেদকে প্রাণীজগৎঅধ্যয়ন করে করে তার থেকে বেছে নিয়ে বিবেচনা করা হয়নি, সমাজে অস্তিত্বশীল বিভিন্ন কুলকেতুগুলিকে কোনো একটা সময় ভগবানের একটা ক্রমিক বিকাশ দেখানোর (কল্পিত) ভাবনা থেকে তার বিভিন্ন স্তরকে কিছু প্রাণীর একটা ক্রম বিকশিত রূপ হিসাবে কল্পনা করা হয়েছিল। এর থেকে বেশি ভাব সম্প্রসারণের উপযোগী তথ্য বিষ্ণুপুরাণে নেই। আপনি যখন সেখানে একটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সন্ধান নেবেন, তখন তো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মেনেই এগোতে হবে, তাই না?
৫) বরাহ থেকে নৃসিংহ কল্পনায় উত্তরণে বা অবতরণেওবিবর্তনের কোনো ছাপ নেই। হিরণ্যকশিপু বধে নৃসিংহের আবির্ভাব দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে হরিণ ও সিংহ—এই দুই কুলকেতু বিশিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে কাহিনিকার দ্বিতীয় গোষ্ঠীর পক্ষে রায় দেওয়াতে পরিণতিতে সেই কথিত দৈত্যকুলাধিপতির মৃত্যু হয়। এর মধ্যে বিবর্তন দেখতে চাইলে কল্পনাকে অনেক দূর প্রসারিত করতে হবে।
৬) অবতারগণ পাখি, বানর, নরবানর, ইত্যাদি রূপ ছাড়াই একবারে যেভাবে মানুষ রূপ গ্রহণ করেছিল, তার মধ্যেও বিবর্তনের কোনো ছাপ নেই। অর্থাৎ, এক ধরনের প্রাণী থেকে অন্য ধরনের প্রাণীর উদ্ভব সংক্রান্ত ভাবনা বিষ্ণুপুরাণের কাহিনিকারের মনে দেখা দিয়েছিল, এমনটা হলে নৃসিংহ নয়, সিংহ রূপ কল্পিত হয়ে তারপর অন্তত পাখি আর বানরের অন্তর্ক্রম প্রত্যাশিত ছিল। কেন না, রাম বা কৃষ্ণ কল্পনার যুগে ভারতে পাখি এবং বানরের কোনোটাই দুর্লভ বা অস্তিত্বহীন ছিল না। সেই কবির চোখে যে অবতার রূপ কল্পনার ক্যানভাসে এরা ঢোকার ছাড়পত্র পেল না, তাতেও মালুম হয় যে এর সঙ্গে বিবর্তন ধারণার কোনো রকম যোগ নেই।
৭) বিবর্তনের বৈজ্ঞানিক ধারণা নিহিত থাকলে কালক্রমে এই অবতার তালিকা বিজ্ঞানের স্বাভাবিক নিয়মেই দশ সংখ্যার মধ্যে সীমিত না থেকে পরবর্তীকালে ধাপে ধাপে সম্প্রসারিত হত, অর্থাৎ, আরও বিভিন্ন অন্তর্বর্তী প্রাণীর নাম সংযোজনের মধ্য দিয়ে তা এক প্রকার সম্ভাব্যতার অর্থে সম্পূর্ণতর হত, যেটা হয়নি।
৮) বিষ্ণুপুরাণ রচিত হওয়ার বহুকাল আগে থেকে শুরু করে তার সমকাল পর্যন্ত প্রাচীন ভারতে বেশ কিছু বিজ্ঞান বিষয়ক পুঁথি রচিত হয়েছিল। সেগুলির কোনোটাতে বিবর্তনবাদ লিপিবদ্ধ না করে একজন বিজ্ঞানী কেন তা বিষ্ণুর অবতার কল্পনার কাব্যিক বয়ানে বয়ন করবেন—এরও একটা পর্যাপ্ত যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দরকার। নয়ত এই তত্ত্বকল্পের কোনো গ্রহণযোগ্যতাই থাকে না, তারপর তো তার সত্যমিথ্যা বিচারের প্রশ্ন।
৯) বস্তুত, সব শেষে বলি, ঊনবিংশ শতাব্দের শেষ ভাগে আমাদের দেশে ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব প্রচারিত হওয়ার আগে পর্যন্ত কোনো সনাতনী প্রবক্তাই বিষ্ণুর দশাবতারের মধ্যে বিবর্তনের ব-ও খুঁজে পাননি।
আপাতত এই কটা কথাই মনে এল।
[৩] পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা
উপরে দেখুন, দশাবতার প্রকল্পনায় বিবর্তনের গল্প না থাকলেও যাঁরা আছে বলে মনে করেন, তাঁদের এটা একটা বিশ্বাস। তাঁদের হাতে উদাহরণ হিসাবে নমুনার সংখ্যা কত? মাত্র তিনটে। এবং এই বিশ্বাসকে তাঁরা কখনও যাচাইয়ের ঘরে নিয়ে যান না। কেন না, সজ্ঞানে না জানলেও বা না মানলেও অগোচরে তাঁরা অবশ্যই এক ভাবে জানেন যে যাচাই করতে গেলে এই বিশ্বাস সাঁইতিরিশ সেকেন্ডও টিকবে না। মুশকিল হচ্ছে, এত অল্প নমুনার ভিত্তিতে একটা এত বড় মাপের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের যে এমনকি সূচনাও করা যায় না, এই বোধটাও তাঁদের মধ্যে কাজ করে না!
কিন্তু আমি এবার পাঠকদের কাছে এর উল্টোপিঠটা তুলে ধরব। চার্লস ডারউইন তাঁর যৌবনেই বিশ্বাস করেছিলেন, জীব জগতে বিবর্তন ঘটেছে। নিজের পিতামহ ইরাসমাস ডারউইন, জ্যাঁ ব্যাপতিস্ত ল্যমার্ক, চার্লস লায়েল ও অন্যান্য অনেকের লেখাটেখা পড়ে এই বিশ্বাস তাঁর জন্মেছিল। তারপর তিনি নিজেই বেরলেন ভূপর্যটনে। নিজ খরচায় বিগ্ল জাহাজে চেপে। পাঁচ বছর (১৮৩১-৩৬) ধরে বিশ্বের প্রায় সমস্ত উপকূল এলাকা থেকে তিনি লক্ষ লক্ষ জীবিত ও জীবাশ্ম নমুনা সংগ্রহ করে আনলেন, যার সাহায্যে প্রায় অনায়াসেই প্রমাণ করা যায়, উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের বিবর্তন হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। ১৮৩৮ সাল নাগাদ বিবর্তন প্রক্রিয়ার (প্রাকৃতিক নির্বাচনের ধারণার ভিত্তিতে) একটা তাত্ত্বিক কাঠামোও তিনি খাতাপত্রে লিখে মোটামুটি দাঁড় করিয়ে ফেললেন। কিন্তু তাঁর সেই ভুবনখ্যাত বইটা—On the Origin of Species by Means of Natural Selection—ডারউইন বের করলেন কবে?
১৮৫৯ সালে। একুশ বছর পরে।
কেন? কেন? এত দীর্ঘ সময় ধরে প্রতীক্ষা করার কী কারণ?
বিশ্বাসের যাচাই, অনুমানের পরখ, তত্ত্বের সাপেক্ষে সামান্যতম সন্দেহও নিরসনের প্রয়াস। আরও পর্যবেক্ষণ করা দরকার। কোথাও কোনো বিরুদ্ধ সাক্ষ্য বা যুক্তি কিংবা বিকল্প ব্যাখ্যা অগোচরে থেকে গেল না তো! কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ করতে কি ভুলে গেলাম? সংগৃহীত তথ্য এবং প্রস্তাবিত যুক্তির মাঝখানে কোনো ফাঁকফোকর থেকে গেল কি?
এক দিকে হচ্ছে তিনটে নমুনার ভিত্তিতে জোরালো দাবি। পুরাণকারের নয়, আধুনিক দাবিদারের।
অপর দিকে হচ্ছে লক্ষ লক্ষ নমুনা হাতে পাওয়ার পরও নিঃসন্দেহ হওয়ার ধৈর্যশীল অপেক্ষা। একজন বিজ্ঞানীর।
এই দুটি ঘটনা সবাইকে বুঝতে হবে। দুরকম মানসিকতা। জ্ঞানের প্রতি দুই ধরনের মনোবৃত্তি। তবেই খুব সহজে ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিশ্বাসের পার্থক্যটা চোখে পড়বে। নয়ত মনে হবে, ও, আপনারাও বিশ্বাস করেন? ডারউইনও বিশ্বাস করেছিলেন? এ বাব্বা, তাহলে আর আমাদের দোষ কী!
আরও মজার কাণ্ড হচ্ছে, সেই ধর্মীয় বিশ্বাসের জোরে দুনিয়া জুড়ে এক বিরাট সংখ্যক ধর্মবিশ্বাসী ডারউইন তত্ত্বের বিরুদ্ধে এক কাট্টা হয়ে হাত পা ছুঁড়ে যাচ্ছে। তারাই আবার উলটে দাবি করছে, বিবর্তনের পক্ষে কোনো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সাক্ষ্য নেই। অতএব এটা বিজ্ঞানের তত্ত্ব হতে পারে না। তত্ত্বটা ভুল। তার মধ্যে বিষ্ণুপুরাণের ভক্তরাও আছে! ইসলামের ভক্তবৃন্দও সেই দাবিতে সোচ্চার।
হা হা হা! অনেক জটিল গম্ভীর কথাবার্তার পর এইখানে এসে কথাটা শুনে একটু অট্টহাসি হেসে নিলে আশা করি আমার এই প্রবন্ধের পাঠকরা সহজ মনে মেনে নেবেন।
তিন খানা নমুনা নিয়ে বিষ্ণুপুরাণের দশাবতার তত্ত্ব বিনা পরীক্ষায় বিবর্তনের বৈজ্ঞানিক ভ্রূণ হতে পারে! কিন্তু লক্ষ লক্ষ নমুনার সাক্ষ্য হাতে নিয়েও ডারউইনের তত্ত্বের সেই সুযোগ নেই। আবার হেসে ফেলছি—হা হা হা!
হাসতে হাসতেই বলছি, ধর্মবিশ্বাসীদের এই কথাটা কিন্তু এই সেদিন অবধিও সত্য ছিল।
সত্যিই বিবর্তন যে হয়েছে, তার সপক্ষে বিজ্ঞানীদের ল্যাবরেটরিতে কোনো পরীক্ষামূলক প্রমাণ ছিল না।
থাকবে কী করে? প্রজাতি রূপান্তরের মাধ্যমে বিবর্তন ঘটতে সময় লাগে লক্ষ লক্ষ থেকে কোটি কোটি বছর। তার পরীক্ষা মানুষ তার ৭০-৮০ বছর বয়সের পরমায়ু নিয়ে কীভাবে করবে? তাই আজ থেকে পঞ্চাশ ষাট বছর আগে অবধিও বিবর্তনের পক্ষে পরীক্ষামূলক প্রমাণ বলতে যা বোঝায় তা ছিল না।
কিন্তু এক দিকে পরীক্ষা পদ্ধতির ও যন্ত্রপাতির নিত্য রূপান্তর, আধুনিক নানা ব্যবস্থার বিকাশ, অপর দিকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব (অণুজীব)—ভাইরাস, ব্যাকটিরিয়া এবং অ্যামিবার মতো আকোষী জীব নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করার সুযোগ বিজ্ঞানীদের হাতে এসে যাওয়ার পর এখন জীবজগতের প্রজাতি রূপান্তর নিয়ে পরীক্ষামূলক সাক্ষ্যপ্রমাণও বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে আমাদের সামনে এসে গেছে। ধর্মবিশ্বাসীদের একমাত্র সত্য অভিযোগটাও অবশেষে হাতছাড়া! হায়!!
কীভাবে এটা সম্ভব হল?
এখানে আবার বিজ্ঞানীদের বিশ্বাসের প্রকরণটা নিয়ে দুচারটে কথা বলি।
বিজ্ঞানে যাকে পরীক্ষা বলা হয় তাও আসলে পর্যবেক্ষণেরই একটা বিশেষ ধরনের তরিকা। নানা রকম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে। সাধারণ মানুষ (তার মধ্যেই সরলমনা ধর্মবিশ্বাসীরাও আছেন) দেখা বলতে যা বোঝেন, বিজ্ঞানে পর্যবেক্ষণ সেই একই জিনিস বোঝায় না। বিজ্ঞানীরা যুক্তি সহ পর্যবেক্ষণ করেন, বিশ্লেষণ করতে করতে পর্যবেক্ষণ করেন। এই জায়গাতেই সাধারণ মানুষের খালি চোখে সূর্য চন্দ্রকে দেখা আর নিকলাস কোপারনিকাস বা গ্যালিলেও গ্যালিলেইয়ের আকাশ দেখার মধ্যে এক সমুদ্র তফাত ঘটে যায়। টেলিস্কোপ ছাড়াই।
চার্লস ডারউইন যন্ত্র দিয়ে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পাননি। এখনকার জীববিজ্ঞানের ছাত্ররা পাচ্ছে। কিন্তু তিনি যুক্তি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। আজীবন। সার্বিক ভাবে। নিরলসভাবে। সেও এক রকমের পরীক্ষাই ছিল। সেই সব পরীক্ষা তাঁর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছিল। আজও করে।
ডারউইন মানুষের একটা মাত্র নমুনা (Homo sapiens) দেখেই ১৮৭১ সালে অন্যান্য বহু আনুষঙ্গিক পর্যবেক্ষণ লব্ধ পরোক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতে মানুষের বানর জাতীয় কোনো আদি পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভবের এক অনুমানসিদ্ধ বিশ্বাস লিপিবদ্ধ করেছিলেন। আজকের পৃথিবীতে হোমো গণভুক্ত অন্তত দশ-বারোটা প্রজাতির জীবাশ্ম পাওয়া গেছে (হ্যাবিলিস, এরগাস্টার, ইরেকটাস, ডেনিসোভান, ফ্লোরেসিয়েন্সিস, অ্যান্টিসেসর, নালেদি, হাইডেলবার্গেন্সিস, লঙ্গি, দ্যালিয়েন্সিস, রুডলফেন্সিস, নিয়ানডারথাল, ইত্যাদি) যা থেকে বোঝা যায়, মানুষ অত সহজে স্যাপিয়েন্স হতে পারেনি। বিবর্তনের অনেকগুলি ধাপ পেরিয়ে তবেই আমরা মানুষ হতে পেরেছি।
আশা করা যায়, ধর্মাশ্রয়ী বিশ্বাসের সঙ্গে বিজ্ঞানীদের যুক্তিতর্ক তথ্যাশ্রয়ী বিশ্বাসের পার্থক্য খানিক পরিষ্কার করতে পেরেছি। আগামী দিনে এ নিয়ে আরও অনেক কথা বলার অবকাশ রইল।֍

 By :
By :