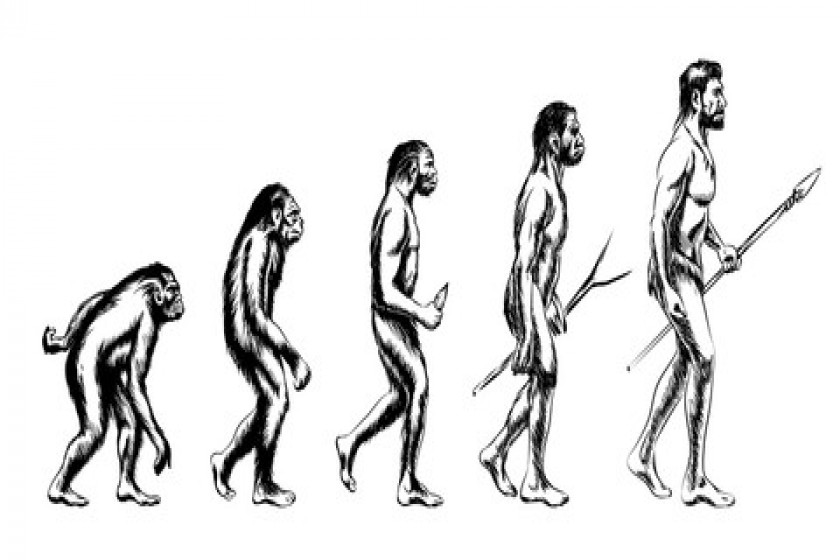http://prehistory2 সমাজ বিকাশের প্রাগৈতিহাসিক স্তরের কথা (দ্বিতীয় পর্ব)
দেবদীপ সিংহ
……… কথা হচ্ছিল শিকারি-সংগ্রাহকদের নিয়ে, এবারে কিছু শিকারি-সংগ্রাহক দলের কথা একটু কাছ থেকে দেখে নেওয়া যাক।
প্রথমে, মন্টেগনিস-নাসকাপি শিকারি-সংগ্রাহকদের কথা।
বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে নৃতাত্ত্বিক এলিয়ানর ব্রুকে লিকক কাজ করছিলেন পূর্ব কানাডার শীতপ্রধান উপদ্বীপ ল্যাবরাডরের মন্টেগনিস-নাসকাপি নামক শিকারি সংগ্রাহকদের উপর। খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে ফ্রান্সের লোকেরা এই অঞ্চলে গিয়েছিল পশু-লোমের ব্যবসা করতে। সেই সময় জেসুইট মিশনারিরাও সেখানে হাজির হয় মন্টেগনিস-নাসকাপিদের মধ্যে ধর্ম প্রচারের তালে। এই মিশনারিদের একজন নেতা ছিলেন লে জোঁ, যার লেখা থেকে লিকক অতীতে মন্টেগনিস-নাসকাপি শিকারি-সংগ্রাহকদের জীবন কেমন ছিল তার ছবি তুলে ধরেছেন। যার থেকে জানা যায়, অতীতে মন্টেগনিস-নাসকাপি শিকারি-সংগ্রাহকরা নানা ধরণের হরিণ, বুনো শূকর, বিভার, ভল্লুক, খরগোশ, সজারু ও এই ধরণের ছোট প্রাণীর শিকার করত, ধরত মাছ আর জলচর পাখি। শিকার করতে তারা ব্যবহার করত তির-ধনুক, বর্শা ও নানা রকমের ফাঁদ। বাড়তি মাংস তারা কাঠের ধোঁয়ায় শুকনো করে জমিয়ে রাখত। গ্রীষ্মকালে তারা সংগ্রহ করত বাদাম, বেরি ও কন্দ।[৬]
তারা তাঁবুতে বাস করত। তাঁবু বানাতে কুড়ি বা ত্রিশটা খুঁটি দিয়ে একটা শঙ্কুর মতো কাঠামো তৈরি করা হতো যেটা ছাওয়াতে ব্যবহৃত হতো বার্চ গাছের ছাল ও পশুর চামড়া। সাধারণত একটা বড় তাঁবুতে তিন চারটে পরিবার একসাথে বাস করত, যারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরস্পরের সাথে আত্মীয় বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। একটা তাঁবুতে ১৫-১৮ জন মতো লোক বাস করতে পারত। মেয়েরা পরিধেয় তৈরি করত পশুর চামড়া দিয়ে। ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচতে তারা চামড়ার তৈরি জুতো পরত। যাতায়াতের জন্য শীতকালে ব্যবহার করত শ্লেজ গাড়ি আর গরমের সময় বার্চ গাছের তৈরি ডোঙা।[৬]
লে জোঁ নামক মিশনারি এই শিকারি-সংগ্রাহদের সাথে ১৬৩৩-১৬৩৪ সালের একটা শীতকাল কাটান। তিনি জানাচ্ছেন তিনটি তাবুর লোকজন মিলে ঠিক করে শীতকালটা তারা একসাথে সেন্ট লরেন্স নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী অঞ্চলে কাটাবে। সেই অনুযায়ী নদীর তীরে ডোঙাগুলো নোঙ্গর করে অববাহিকার ভিতরের দিকে তারা চলতে থাকে এবং নভেম্বরের ১২ তারিখ থেকে এপ্রিলের ২২ তারিখের মধ্যে ২৩ বার তাদের বাসা স্থানান্তরিত করে। সে বছরের শীতকালটা তাদের ভাল যাচ্ছিল না, বরফ কম পড়ায় বন্য হরিণের দলগুলোকে খুঁজে পেতে অসুবিধা হচ্ছিল। তিনটে তাঁবুর মধ্যে তাই একটা তাঁবুর লোকজন বাকিদের ছেড়ে যাবে ঠিক করে, যাতে তারা বেশি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে। ঘটনাচক্রে একসময় ভারী তুষারপাত হলে পরিস্থিতির উন্নতি হয়, প্রচুর শিকার মেলে, ফলে কিছু মাংস তারা শুকিয়ে মজুত করতে পারে। বসন্তকাল এলে, লে জোঁ যে তাঁবুতে থাকছিল তার লোকজন সাময়িক ভাবে বিভক্ত হয়ে যায়, কিছু জন উচ্চ ভূমির দিকে চলে যায় হরিণ শিকার করতে, বাকিরা নদীর ধার বরাবর যায় বিভার পাওয়ার আশায়। শেষে আবার একদিন সবাই নদীর সেই তীরে এসে মিলিত হয়, যেখানে নৌকাগুলো লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। [৬]
মন্টেগনিস-নাসকাপিদের সামাজিক মূল্যবোধ দাবি করে উদারতা, শেখায় মিলেমিশে কাজ করতে ও ধৈর্যশীল হতে, লে জোঁ তাদের প্রতিদিনের জীবনে রসবোধ, পরস্পরকে হিংসা না করা ও একে অপরকে সহায়তা করার অভ্যাসের কথা বলেছেন।
মন্টেগনিস-নাসকাপি শিকারি-সংগ্রাহকদের বৈবাহিক জীবন সম্পর্কে জানা যায় জেসুইট মিশনারিদের বর্ণনা থেকে। তাদের মধ্যে খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচারের প্রশ্নে লে জোঁর সামনে প্রধান বাধা হয় "Montagnais' unquestioned acceptance of divorce at the desire of either partner, of polygyny, and of sexual freedom after marriage. ” লে জোঁ বলছেন "The young people do not think that they can persevere in the state of matrimony with a bad wife or a bad husband," এবং "They wish to be free and to be able to divorce the consort if they do not love each other" । তিনি আরও বলছেন "The inconstancy of marriages and the facility with which they divorce each other, are a great obstacle to the Faith of Jesus Christ. We do not dare baptize the young people because experience teaches us that the custom of abandoning a disagreeable wife or husband has a strong hold on them"।[৬]
বহুগামীতার প্রশ্নে মন্টেগনিস-নাসকাপিদের মধ্যে কোন অনুশাসন নেই। এ সম্পর্কে লে জোঁর অভিজ্ঞতা: "Since I have been preaching among them that a man should not have more than one wife, I have not been well received by the women; for, since they are more numerous than the men, if a man can only marry one of them, the others will have to suffer. Therefore this doctrine is not according to their liking"। লে জোঁ যখন এক মন্টেগনিস-নাসকাপি পুরুষকে খ্রিষ্ট ধর্মের নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন তখন যে উত্তর তিনি পান সেটা বেশ চমকপ্রদ। লে জোঁ লিখছেন: “I told him that it was not honorable for a woman to love any one else except her husband, and that this evil being among them, he himself was not sure that his son, who was there present, was his son.” সেই পুরুষ উত্তরে জানায় : "Thou hast no sense. You French people love only your own children; but we all love all the children of our tribe." [৬]

মন্টেগনিস-নাসকাপিদের পর এবার দেখে নেওয়া যাক !কুং-দের জীবন (শুরুতে থাকা “!” চিহ্ন একটি ক্লিক শব্দ, যা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলিতে নেই।)
আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ দিকে বতসোয়ানা ও নামিবিয়ার সীমান্তরেখা বরাবর বিস্তীর্ণ কালাহারি মরুভূমিতে দেখা যায় সান নামক শিকারি সংগ্রাহকদের। এই সানদের মধ্যে একটি গোষ্ঠী হল !কুং। কালাহারির রুক্ষ কৃপণ পরিবেশেও !কুং -রা কিন্তু বেশ চমৎকার মানিয়ে নিয়েছে। এদের একেকটা ব্যান্ডে থাকে ত্রিশ জন করে, মোটামুটি ছয়টি পরিবার, যারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরস্পরের সাথে আত্মীয় বন্ধনে আবদ্ধ। গ্রীষ্মকালে, অক্টোবর থেকে মে মাস অব্দি, এই একেকটা ব্যান্ড মোঙ্গাঙ্গো বৃক্ষকে আশ্রয় করে তাদের অস্থায়ী গৃহগুলো নির্মাণ করে, যা কয়েক সপ্তাহ অন্তর অন্তর তারা পরিবর্তন করে। এক জায়গায় বেশি দিন না থাকার পেছনে থাকে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা, খাবার সংগ্রহের বৃত্তটিকে তারা বড় করতে চায় না। ব্যান্ডগুলো পরস্পরের সাথে আদানপ্রদানের উষ্ণ সম্পর্ক বজায় রাখে। শুষ্ক শীতকালে কোন স্থায়ী জলের কূপের চারপাশে অনেকগুলো ব্যান্ড একসাথে মিলিত হয়। তখন তাদের লোকসংখ্যা হয় একশোর অধিক। যদিও জনঘনত্ব বেড়ে যাওয়ায় তাদের খাদ্য সংগ্রহ করতে বেশ কষ্ট হয়, তবুও এই সময়টা তাদের সামাজিক মেলামেশার সময়। এই সময় তারা ব্রত-পার্বণ পালন করে, বন্ধু পাতায়, বিবাহের জন্য পাত্র পাত্রী নির্বাচন করে, নাচে গানে মেতে ওঠে, বয়স্করা গল্প বলে, সকলের মধ্যে নানান উপহারের আদান প্রদান হয়। এরপর বর্ষা এলে আবার তারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বেরিয়ে পড়ে, যদিও ব্যান্ডের গঠন আর আগের গ্রীষ্মের মত থাকে না। পুরনো কেউ বেরিয়ে যায় নতুন কেউ আসে। নিজের পছন্দ মতো তারা দল নির্বাচন করে। কোন ঝগড়া বিবাদ থাকলে এই সময় তার নিষ্পত্তি হয়ে যায়।
শিকারযোগ্য পশু হিসাবে কালাহারির এই অঞ্চলে পাওয়া যায় আফ্রিকার বুনো দাঁতাল শুয়োর, নানা ধরণের অ্যান্টিলোপ, জিরাফ, ইল্যান্ড, জেবরা, কুডু, জেমসবক, বাফেল। শিকারের কাজ করে ছেলেরা। তাদের হাতিয়ারের মধ্যে থাকে মুগুর ও তির-ধনুক। তিরের ডগায় তারা পতঙ্গের লার্ভা থেকে প্রাপ্ত বিষ মিশিয়ে নেয়। এছাড়া খরগোশ ও ছোট প্রাণী ধরতে তারা ফাঁদ পাতে, গর্ত থেকে খরগোশকে তুলতে একরকমের বড়শির ব্যবহার করা হয়। মাল-পত্র বইতে নেয় প্রাণীর পেশীতন্তু দিয়ে তৈরি করা জালের ব্যাগ। শিকার থেকে আসে খাবারের ৩০-৪০ শতাংশ। সংগ্রহের কাজ করে মেয়েরা। সংগ্রহের উপকরণ বলতে থাকে লাঠি ও পশুচামড়া দিয়ে তৈরি ঝোলা যাতে তারা বাদাম, ফল, মূল, কন্দ, বেরি এইসব সংগ্রহ করে। সংগ্রহের কাজে চলার সময় মেয়েরা ছোট শিশুকে পিঠে বেঁধে নেয়, মেয়েরা সাধারণত তিন বা চার বছর অন্তর একবার সন্তান ধারণ করে। !কুং -রা দু’শর উপর উদ্ভিদ প্রজাতির সাথে পরিচিত, তাদের নামকরণও তারা করেছে; এর বেশিরভাগই তারা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে।
দেখা গেছে ছেলেরা সপ্তাহে গড়ে ২১ ঘন্টা শিকারের কাজ করে। মেয়েদের ক্ষেত্রে, সপ্তাহে সংগ্রহের কাজের সময়টা বারো ঘন্টার কিছু বেশি যা থেকে আসে খাদ্যের ৭০ শতাংশ। গৃহকর্ম ও হাতিয়ার তৈরির কথা ধরলে, ছেলেদের সাপ্তাহিক কাজের ঘন্টা দাঁড়ায় চুয়াল্লিশ, যা মেয়েদের ক্ষেত্রে হয় চল্লিশ ঘন্টার মতো। কিন্তু বাচ্চাদের দেখাশোনার দায়িত্ব মূলত মেয়েরাই পালন করে, তাই সাপ্তাহিক কর্মের সময় ছেলেদের থেকে মেয়েদের বেশি হয়। সমাজের মেয়েরা মুক্ত ও স্বাধীন, যথেষ্ট সম্মানও তারা লাভ করে।
!কুং -দের বিবাহ প্রথমে ঠিক করে পাত্র ও পাত্রীর মা-বাবারা। বিয়ে সাধারণত নিকট আত্মীয়ের মধ্যে হয় না। পরিবারের দিক থেকে বিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য থাকে সামাজিক সম্পর্ক ও আদান-প্রদান বাড়ানো। বিবাহের অনুষ্ঠান বলতে পাত্র ও পাত্রীর বাড়ির লোকেরা নব দম্পতির জন্য একটা কুঁড়ে নির্মাণ করে দেয়, তারপর পাত্র ও পাত্রীকে সেখানে আনা হয়। এই কুঁড়ে সাধারণত মেয়ে যে ব্যান্ডে থাকে সেখানেই বানানো হয়, তারপর থেকে তারা সেখানেই থাকতে শুরু করে। তবে সুবিধামতো ছেলের ব্যান্ডেও তারা কুঁড়ে নির্মাণ করে থাকতে পারে। এই বিয়ে প্রথমে হয় পরীক্ষামূলক। মেয়ের পাত্র পছন্দ না হলে বা তাদের মধ্যে বনিবনা না হলে বিবাহ ভেঙে যায়, ছেলে নিজের বা অন্য ব্যান্ডে গিয়ে যোগ দেয়। এরপর তারা আবার বিবাহ করতে পারে, সেটা পরিবারের লোকের উদ্যোগেও হতে পারে বা নিজেরাও পছন্দ করে করতে পারে। বিবাহের পাত্র নির্বাচন করার ক্ষেত্রে দেখা হয় ছেলে শিকার করার ও পরিবারের দায়িত্ব নেওয়ার উপযুক্ত কিনা। সাধারণত নারী-পুরুষ সকলেই অনেকবার বিয়ে করে, বিবাহের বাইরেও প্রভূত যৌন স্বাধীনতা তাদের থাকে। সতীত্বের কোন ধারণা তাদের মধ্যে নেই। এক নৃতাত্ত্বিক দেখেছেন, সতীত্ব বা অনুরূপ কোন শব্দ তাদের শব্দ ভাণ্ডারে নেই। ব্যান্ডে প্রতিটা পরিবারের আলাদা কুঁড়ে থাকে, যেখানে স্বামী-স্ত্রী ও বাচ্চারা বাস করে। [৭, ৮, ৯, ১০]
দুটি শিকারি-সংগ্রাহক দলের কথা আমরা একটু কাছ থেকে দেখলাম। খুঁটিনাটিতে শিকারি-সংগ্রাহকদের সমাজে কিছু পার্থক্য থাকলেও, কয়েকটা লক্ষ্য করার মতো বিষয় তাদের সমাজে নেই এবং সেটা সকল শিকারি-সংগ্রাহক সমাজেরই একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য:
১) অর্থনৈতিক বৈষম্য নেই। আধুনিক অর্থে ব্যক্তি সম্পত্তি বলতে যা বোঝায়, তা অনুপস্থিত।
২) নারী-পুরুষের মধ্যে সামাজিক বিভেদ নেই।
৩) রাষ্ট্র নেই, মানুষের উপর মানুষের জোর-জুলুম বা শোষণ নেই। সামাজিক স্তরেও উচ্চ-নীচ নেই।
৪) প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম নেই।
আমাদের সমাজে যে জিনিসগুলোকে আজ একটা ব্যাধি বলে মনে হয় তার কোনটাই এদের সমাজে দেখা যায় না। পৃথিবীর যে কোনো অঞ্চলের, যে কোনো শিকারি-সংগ্রাহক দলই হোক, এই বিষয়গুলো তাদের মধ্যে নেই। ফলে এটা একটা আকস্মিক ঘটনা হতে পারে না। আবার পৃথিবীর সকল অঞ্চলের শিকারি-সংগ্রাহকদের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে বৈচিত্র সত্ত্বেও সামগ্রিক অর্থে একটা সাদৃশ্য দেখা যায়। এর ব্যাখ্যা কী? মার্কস বলছেন:
" মানব-জীবনের সামাজিক উৎপাদনের মধ্যে মানুষ জড়িত হয় কতগুলি অনিবার্য ও ইচ্ছা-নিরপেক্ষ নির্দিষ্ট সম্পর্কে, উৎপাদন-সম্পর্কে, যা মানুষের বৈষয়িক উৎপাদন-শক্তির বিকাশের একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ের অনুরূপ। এই উৎপাদন-সম্পর্কগুলির সমষ্টি হল সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো, সেই আসল বনিয়াদ, যার উপর গড়ে ওঠে আইনগত আর রাজনৈতিক উপরিকাঠামো এবং সামাজিক চেতনার নির্দিষ্ট রূপগুলি হয় তারই অনুরূপ । বৈষয়িক জীবনের উৎপাদন-পদ্ধতিই সাধারণভাবে মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন-প্রক্রিয়াকে নির্ধারণ করে। মানুষের সত্তা তার চেতনা দ্বারা নির্ধারিত নয়, বরং ঠিক বিপরীতভাবে, মানুষের সামাজিক সত্তাই নির্ধারন করে তার চেতনাকে।" [১১]
শিকারি-সংগ্রাহকদের সমতা ভিত্তক সমাজ সংগঠনের আসল কারণটা তাদের বৈষয়িক জীবনের দিকে দৃষ্টি দিলে সহজেই বোঝা যায়। মানব সমাজে উৎপাদনের জন্য লাগে শ্রম, শ্রমের উপকরণ ও শ্রমের বিষয়। শ্রমের বিষয় হলো যার উপর শ্রম ক্রিয়া করে, আর শ্রমের উপকরণ হলো সেই সবকিছু যার দ্বারা শ্রম, শ্রমের বিষয়ের উপর ক্রিয়া করে তার রূপান্তর ঘটায়। এই দুটো একসঙ্গে গঠন করে উৎপাদন উপকরণ (শ্রমের উপকরণ + শ্রমের বিষয়)। সৃজনশীল হাতিয়ারধারী মানুষ হলো উৎপাদিকা শক্তি (শ্রমশক্তি+শ্রমের হাতিয়ার)। শ্রমের বিষয় জোগায় প্রকৃতি। শিকারি-সংগ্রাহকদের ক্ষেত্রে তা হলো আশপাশের বন-জলা-জঙ্গল। শিকারি-সংগ্রাহকদের শ্রম প্রাথমিক পর্যায়ের এবং শ্রমের উপকরণ, মূলত শ্রমের হাতিয়ার, সরল প্রকৃতির: সংগ্রহ ও শিকারের কাজে আসে এমন হাড়, লাঠি আর পাথরের জিনিস। এই পর্যায়ে হাতিয়ারধারী শিকারি-সংগ্রাহকদের উৎপাদিকা শক্তি তাই সরল ও অনুন্নত, শ্রম বিভাজন প্রাকৃতিক ধরণের, মূলত বয়স ও লিঙ্গের উপর ভিত্তি করে। এই অবস্থায় খুব স্বাভাবিক ভাবেই আশপাশের প্রকৃতি অর্থাৎ বন-জঙ্গল-জলা-জমির উপর কারো কোন বিশেষ অধিকার থাকতে পারে না, থাকেও না। এদের প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক পুরুষ শিকারি ও প্রত্যেক মহিলা সংগ্রাহক। যা কিছু যৌথ শ্রমের ফসল তাতে থাকে সবার অধিকার । যদিও ব্যবহৃত হাতিয়ার ও পোশাক-আশাক ইত্যাদির উপর ব্যক্তিগত অধিকার থাকে তবুও এই জিনিসগুলো এতোই সরল প্রকৃতির যে তার বিশেষত্ব কিছু মাত্র নেই। যে কেউ প্রয়োজন মতো এগুলো যখন খুশি প্রাকৃতিক উপাদান (যাতে কারো কোন বিশেষাধিকার নেই) ব্যবহার করে বানিয়ে নিতে পারে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে যা শিকার বা জোগাড় হয় তা বাড়তি হলে অন্য পরিবারের সাথে তারা ভাগ করে নেয়। কারণ প্রধানত অনিশ্চয়তা; আজ যে বা যারা বেশি কিছু পেল কাল দেখা যাবে তারা হয়তো কিছুই পেল না। এছাড়া রোগ-জ্বালার বিষয় থাকে, সবাই সবদিন কাজে যেতে পারবে তেমন নয়। ভাগাভাগির মাধ্যমে তারা এই অনিশ্চয়তাকে নিশ্চয়তায় রূপান্তরিত করে নেয়। ফলে এদের মধ্যে ভাগাভাগির এক ঐতিহ্যবাহী প্রথা দেখা যায়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা সাধারণ চোখে বেশ বাড়াবাড়ি রকমের মনে হতে পারে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সামাজ সৃষ্ট বিভেদ কিছু নেই, যেটুকু আছে তা প্রাকৃতিক। ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই এদের সমাজে ধনী-দরিদ্র নেই, উচ্চ-নীচ নেই।
উৎপাদিকা শক্তি অনুন্নত হওয়ায় উদ্বৃত্ত বলে কিছু নেই, সঞ্চয়ের প্রশ্নও নেই, উপায়ও খুব একটা নেই। আসলে এদের জীবনের মূল মন্ত্র হল গতি। বারবার তারা খাবারের খোঁজে স্থান পরিবর্তন করে, ফলে তারা থাকতে চায় ঝড়ঝড়ে, একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোই তারা সঙ্গে রাখে। সঞ্চয়ের প্রবণতা তাদের কাছে বিড়ম্বনা। ছেলেরা হয়ত সঙ্গে নেয় তির ধনুক আর পাথরের হাতিয়ারগুলো; মেয়েদের কোলে কখন বা পিঠে বাঁধা থাকে বাচ্চারা, মাথায় আর হাতে তারা নেয় অন্য কিছু জিনিস। এই যাযাবর জীবনের জন্যই এদের সন্তান উৎপাদনের প্রবণতা কম, দলের আকার খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে না। হাতিয়ার দুর্বল হওয়ায় খাবার জোগাড় ও আত্মরক্ষার প্রশ্নে এরা সকলে সকলের উপর নির্ভরশীল।
বিশেষ মালিকানা না থাকা ও উৎপাদন কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করা হলো শিকারি-সংগ্রাহকদের উৎপাদিকা শক্তির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ উৎপাদন সম্পর্ক, যা গঠন করেছে এদের অর্থনীতির ভিত্তি। এই ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে এদের সমাজিক চিন্তা ভাবনা, নানান প্রথা ও রীতি। তাই দেখা যায় মানসিক গুণের মধ্যে লালিত হয় উদারতা, বিনয়, অপরকে সাহায্যের প্রবণতা। অহংবোধ বা স্বার্থপরতা তাদের জীবনেরই পরিপন্থী, বেঁচে থাকার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ নয়। একদিকে শিকার অনিশ্চিত কিন্তু যখন পাওয়া যায় তা জোগায় প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবার, অন্যদিকে জোগাড়েদের কাছ থেকে আসে প্রতিদিনের খাবারের নিশ্চয়তা। ফলে শিকারিরা নির্ভর করে সংগ্রাহকদের উদারতার উপর আর শিকারিদের হতে হয় বিনয়ী। নৃবিজ্ঞানী রিচার্ড লি কালাহারির শিকারি-সংগ্রাহক !কুংদের সম্পর্কে বলছেন:
“!কুং সম্প্রদায়ের মানুষ অত্যন্ত সমতাবাদী, এবং তারা এই সমতা বজায় রাখার জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক প্রথার বিকাশ ঘটিয়েছে। প্রথমে, অহঙ্কারী এবং গর্বিতদের নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং তারপর সেই দুর্ভাগা মানুষদের আবার সুযোগ দেওয়া হয়। পুরুষদের শিকার করতে উৎসাহিত করা হয়, কিন্তু সফল শিকারির সঠিক আচরণ হল বিনয় এবং সংযম।” [২]
একজন !কুং নিজেদের একটি প্রথা সম্পর্কে নিচের কথাগুলো জানায়:
" ধরা যাক, একজন পুরুষ শিকার করতে গিয়েছে। তার বাড়িতে এসে গর্বিতভাবে ঘোষণা করা উচিত নয়, “আমি জঙ্গলে একটি বড় শিকার পেয়েছি!” প্রথমে তাকে চুপচাপ বসে থাকতে হবে যতক্ষণ না আমি বা আর কেউ তার আগুনের কাছে এসে জানতে চায়, “তুমি আজ কী করছিলে?” সে শান্তভাবে উত্তর দেবে, “আহ, আমি শিকার করতে ভাল পারি না। আমি কিছুই দেখিনি... হয়তো ছোট কিছু একটা।” তখন আমি হাসি, কারণ আমি জানি সে বড় কিছু শিকার করেছে।” [২]
নারী-পুরুষের মধ্যে শ্রমবিভাজন থাকলেও, সামাজিক গুরুত্বের দিক থেকে মেয়েদের কাজের অবদান পুরুষদের থেকে কোন অংশে কম নয়, উপরন্তু মেয়েরা সন্তানের জন্ম দেওয়া ও লালন পালনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে যা দলটির টিকে থাকার একটি প্রয়োজনীয় শর্ত। ফলে এই সমাজে মেয়েদের মর্যাদাহীনতার বা পরাধীনতার কোন প্রশ্ন আসে না।
এদের সমাজ সংগঠন সরল প্রকৃতির, মুক্ত ও স্বাধীন। বড় কোন ঝগড়া বা বিবাদ দেখা দিলে এক দল বা ব্যান্ড ত্যাগ করে অন্য দলে যোগ দেওয়ার মধ্যে দিয়ে সমস্যার সহজ সমাধান হয়ে যায়। এমন সমাজে রাষ্ট্র দূর, রাজনৈতিক সংগঠনও প্রায় অনুপস্থিত। সমাজের প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষ সকলে মিলে ঠিক করে নিজেদের কাজ কারবার। আনুষ্ঠানিক অর্থে নেতা বা দলপতি বলে কেউ থাকেনা। যেখানে কিছুটা নেতার ভূমিকা আছে সেটাও কর্তৃত্বের দ্বারা নয় বরং বাড়তি দায়িত্ব ও উদাহরণ সৃষ্টির দ্বারা। সমাজে নারী-পুরুষ সকলেই স্বাধীন, তাদের সমাজ চলে সমতার উপর ভিত্তি করে।
শিকারি-সংগ্রাহকদের প্রকৃতি ও জীবন সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা প্রকৃতিবাদ পর্যায়ের। মানুষ এই পর্যায়ে নিজেকে প্রকৃতি থেকে, তার চারপাশের গাছপালা, জীবজন্তু, পাহাড়, নদী, বন, জঙ্গল থেকে পুরোপুরি আলাদা করতে পারেনি। সব কিছুর উপরেই সে মানবিক বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছে। প্রাণকে সে ব্যাখ্যা করেছে আত্মা নামক এক কাল্পনিক সত্তা দিয়ে। তাদের কাছে এই আত্মা কিন্তু অতিপ্রাকৃত কিছু নয়। মানুষ নিজেদেরকে যেহেতু প্রকৃতি থেকে পুরোপুরি আলাদা করতে পারেনি, তাই জীবনকে যেমন সে আত্মা দিয়ে ব্যাখ্যা করেছে প্রাকৃতিক শক্তির উপরেও তেমনি আরোপ করেছে আত্মাকে। আত্মাকে ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে প্রাকৃতিক ও সামাজিক নানান ঘটনাকে নিজেদের অনুকূলে আনা সম্ভব- এমনটা তারা মনে করে। এই আত্মার জগতকেও তারা কল্পনা করেছে নিজেদের সমাজেরই প্রতিরূপে। এই আত্মাকে ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তারা মিলিতভাবে নানারকম ক্রিয়ামূলক আচার পালন করে, যাকে বলা হয় ম্যাজিক। শিকারি-সংগ্রাহকদের ম্যাজিকে তাদের মূল জীবিকা শিকার ও সংগ্রহের সাথে যুক্ত নানা ধারণার ছাপ পাওয়া যায়। রোগ মুক্তির জন্য বা অন্যান্য কারণে ম্যাজিক পালন করা হয়। ম্যাজিক একটা সামাজিক ক্রিয়া, যদিও ওঝা (medicine man) থাকে কিন্তু সেটা কোন বিশেষ পদ নয়। যে কেউ উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নিয়ে ওঝা হতে পারে। এই ম্যাজিক পর্যায়ের চিন্তাভাবনার মধ্যে অতিপ্রাকৃত সত্তার যেমন কোন স্বীকৃতি নেই তেমনি আবার তার মধ্যে বাস্তব জগত যে নিয়ম শাসিত তারও কোন স্বীকৃতি থাকে না।
শিকারি-সংগ্রাহকদের পারিবারিক গঠন সম্পর্কে বুঝতে হলে সাধারণভাবে পরিবারের ইতিহাস সম্পর্কে কিছু কথা বুঝে নেওয়া দরকার। এঙ্গেলস তার " পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি" বইতে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ভিত্তিতে এই বিষয়ে মূল দৃষ্টিভঙ্গিটা দিয়ে গেছেন। তবে যে সময়ে তিনি বইটা লিখেছেন সে সময়ে এই সকল বিষয়ে অনুসন্ধান খুব বেশি এগোয়নি, ওনাকে কাজ করতে হয়েছে অপ্রতুল তথ্যের উপর নির্ভর করে। ফলে খুঁটিনাটিতে কিছু সীমাবদ্ধতা সেখানে থেকে গেছে, যেমনটা বিজ্ঞানের যে কোন শাখার ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বইটা লেখার একশো বছর পরেও যে এর গুরুত্ব কমেনি সেটা একদিকে এঙ্গেলসের অসাধারণ প্রতিভা ও অন্তর্দৃষ্টির আর অন্যদিকে তাঁর পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক।
মানুষ যখন পশু জগত থেকে বেরিয়ে আসেনি, হাতিয়ার তৈরি করতে সক্ষম হয়নি, তখনও সে বংশবৃদ্ধি করেছে, নিজেদের টিকিয়ে রেখেছে। ফলে মানুষের জৈবিক উৎপাদন তার সামাজিক উৎপাদনের চেয়ে প্রাচীন। সামাজিক উৎপাদন শুরু হওয়ার পর থেকে মানুষের জৈবিক উৎপাদনও ধীরে ধীরে সমাজিক উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণাধীনে এসেছে। বৈষয়িক উৎপাদনের বিকাশের সাথে তাল রেখে মানুষের জৈবিক সম্পর্ক, তার পরিবারের রূপও বদলে গেছে। এইভাবে মানুষের উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের স্তরগুলোর সাথে একেকটা পরিবার রূপকে চিহ্নিত করা সম্ভব। উৎপাদন ক্রিয়া যত প্রাথমিক পর্যায়ের মানুষের যৌন সম্পর্ক ততো প্রাকৃতিক ধরণের। দীর্ঘ পুরা-প্রস্তর যুগ ধরে মানুষের যৌন সম্পর্কের রূপের কি রকম বিকাশ ঘটেছে সে সম্পর্কে নথি তেমন কিছু নেই। যেটুকু তথ্য প্রমাণ এখন পাওয়া যায় তার থেকে মনে হয় প্রাগৈতিহাসিক স্তরে এঙ্গেলস যতটা মনে করেছিলেন, প্রাকৃতিক কারণের চেয়ে সামাজিক শক্তির প্রভাব তার থেকে বেশি কার্যকর ছিল। কিন্তু এঙ্গেলসের সময় এই বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু বলার মতো তথ্য তেমন ছিল না।
মর্গান বা এঙ্গেলসের সময় শিকারি-সংগ্রাহকদের উপর কাজ হয়েছিল খুব কম। ফলে শিকারি-সংগ্রাহকদের জীবন সম্পর্কে তাদের হাতে তথ্য প্রায় কিছুই ছিল না। ইরকোয়াস, যাদের সাথে মর্গানের প্রত্যক্ষ ও অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল তারা আটকে ছিল প্রাথমিক কৃষির স্তরে। মর্গান আত্মীয়তা সম্পর্কের নামগুলোকে শিলীভূত পুরনো যৌন সম্পর্কের রূপ হিসাবে ধরেছিলেন। এই পদ্ধতিতে নিম্মলিখিত পরিবারের রূপগুলোর কথা তিনি বলেছেন:
১) এক রক্ত সম্পর্কের পরিবার: এক প্রজন্মের নারী-পুরুষের সাথে পরের প্রজন্মের পুরুষ-নারীর বিবাহ নিষিদ্ধ।
২) পুনালুয়া পরিবার: মায়ের দিক থেকে একই বংশ ধারার ভাই ও বোনের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ।
৩) জোড় বাঁধা পরিবার: পিতৃ ও মাতৃ উভয় ধারার ভাই ও বোনের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ।
৪) এক পতি-পত্নী পরিবার: বহুবিবাহ নিষিদ্ধ।
১ থেকে ৩ অবধি, একেকটা নিষেধ সমাজের মধ্যে কিছু বৈবাহিক গোষ্ঠী সৃষ্টি করছে। নারী-পুরুষ উভয় দিক থেকে একের অধিক বিবাহের ক্ষেত্রে তেমন কোন আপত্তি নেই, শুধু সেটা বৈধ বৈবাহিক গোষ্ঠীর মধ্যে হতে হবে । চার নম্বর বিন্দুতে এসে একের বেশি বিবাহের ক্ষেত্রে আপত্তি আসছে, যদিও তা বাস্তব ক্ষেত্রে শুধু মেয়েদের জন্য। উপরের ব্যাখ্যাটা যা এঙ্গেলসও গ্রহণ করেছেন সেই সম্পর্কে আধুনিক গবেষণার আলোকে দুটি বিষয় সঠিকভাবে বুঝে নেওয়া দরকার।
ক) মর্গানের "আত্মীয়তা সম্পর্কের নামগুলোকে শিলীভূত পুরনো যৌন সম্পর্কের রূপ”-এই প্রকল্পটা বর্তমানে আর স্বীকৃত নয়। যদিও বৈধ "বৈবাহিক গোষ্ঠী" ‘র ক্ষেত্রে নিষেধের বৃদ্ধি পাওয়াটা মোটের উপর ঠিক আছে।
খ) এঙ্গেলস এক পতি-পত্নী পর্যায়ে উত্তরণের সঠিক ব্যাখ্যা দিলেও তার আগের পর্যায়ে "বৈবাহিক গোষ্ঠী" সৃষ্টির পেছনে নানা বিধি নিষেধের উৎপত্তির কারণের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটা আর গ্রহণ যোগ্য নয়। এই বিষয়ে মর্গান প্রাকৃতিক নির্বাচনের কথা বলেছেন। এঙ্গেলসের ব্যাখ্যাও অনেকটা সেইরকম: “Natural selection, with its progressive exclusions from the marriage community, had accomplished its task; there was nothing more for it to do in this direction. Unless new, social forces came into play, there was no reason why a new form of family should arise from the single pair.” [১]
বর্তমানে গবেষণায় দেখা গেছে আত্মীয়তার সম্পর্কগুলো সামাজিক দায়-দায়িত্ব বোঝায়, জীবজনিত সম্পর্ক নয়। বিবাহের প্রশ্নে শিকারি-সংগ্রাহকদের মধ্যে নিষেধের বেড়াজাল প্রায় নেই বা থাকলেও তা দুর্বল। কৃষিভিত্তিক গ্রাম সমাজ পত্তনের পর যখন সামাজিক জটিলতা বৃদ্ধি পায় এবং সমাজকে নতুন করে সংগঠিত করার দরকার পরে তখন বৈবাহিক গোষ্ঠীর আকারে সমাজ সংগঠিত হয়। বংশধারা বা গোত্র (clan) প্রথা বেশি করে চালু হয়, বিবাহের প্রশ্নে নানান বিধি নিষেধ আসতে থাকে যেখানে একই বংশধারার মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হয়। যার মূলে প্রেরণা ছিল অর্থনৈতিক, বিবাহের মাধ্যমে জ্ঞাতি সম্পর্ক বাড়ানো হয়, যারা পরস্পরের সাহায্যকল্পে বাধ্য থাকে। যাই হোক, এইটুকু বিষয় শুধরে নিলে এরপর এঙ্গেলস যা বলছেন তাকে আধুনিক গবেষণাও সমর্থন করছে: “We thus have three principal forms of marriage which correspond broadly to the three principal stages of human development. For the period of savagery, group marriage; for barbarism, pairing marriage; for civilization, monogamy…….” [১]
শিকারি সংগ্রাহকদের মধ্যে এই "group marriage” বলতে বুঝতে হবে শিথিল একগামীতা ও তার সাথে মাঝে মাঝে বহুগামীতা। এঙ্গলসও সেই ভাবেই একে ব্যাখ্যা করেছেন। শিকারি সংগ্রাহকদের পরিবার সম্পর্কে আরেকটা বিষয় মনে রাখা দরকার। উপর উপর দেখলে মনে হতে পারে শিকারি সংগ্রাহকদের পরিবার অনেকটা আধুনিক নিউক্লিয়াস পরিবারের মতোই। কিন্তু শিকারি সংগ্রাহকদের পরিবার তাদের ব্যান্ডের সাথে নিবিড় ও অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। ব্যান্ডের বাইরে তাদের স্বাধীন বা সক্রিয় অস্তিত্বের কথা কল্পনাই করা যায় না। সমাজের মধ্যে এই পরিবারগুলো সক্রিয় হয়ে উঠবে আরো পরে, উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের সাথে তাল রেখে ধাপে ধাপে।
শিকারি ও সংগ্রাহকদের জীবনের কিছু সাধারণ দিকই এখানে তুলে ধরা গেল। মানুষের সমাজ কিন্তু এই স্তরেই আটকে থাকেনি। আজ থেকে আনুমানিক ১০ হাজার বছর আগে নব্য প্রস্তর যুগের সময় থেকে কিছু মানুষের দল প্রথম কৃষিকাজ ও পশুপালন শেখে। যাযাবর জীবন-যাত্রার জায়গায় গড়ে তোলে গ্রাম ভিত্তিক সমাজ। এর পাশাপাশি শুধুই পশুপালক যাযাবর উপজাতি সমাজগুলোরও আগমন ঘটে। এরও কয়েক হাজার বছর পর, আজ থেকে আনুমানিক ৬ হাজার বছর আগে তাম্র-প্রস্তর যুগে প্রথম গড়ে উঠে নগর কেন্দ্রিক সভ্যতা, প্রকৃত অর্থে এই স্তরেই মানব সমাজ প্রথম অর্থনৈতিক শ্রেণীতে ভাগ হয়ে যায়। কৃষিকাজ শেখার পর ও নগর সভ্যতা গড়ে ওঠার আগে, মাঝের একটা দীর্ঘ সময়েও সমাজ অর্থনৈতিক শ্রেণীতে ভাগ হয়ে যায়নি এবং মানব সমাজের এই পর্যায়ও প্রাক-ইতিহাসেরই অন্তর্গত (যদিও বর্তমান লেখায় এই পর্যায় সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করা গেল না) । এই পর্যায়কে বলা যায় নিঃশ্রেণীক সমাজ থেকে শ্রেণী সমাজের দিকে যাত্রার অন্তর্বর্তীকালীন সময়। শ্রেণী-সমাজের উপাদানগুলো এই সময় বিকশিত হতে থাকে। এই বিকাশের গতি পথে, ঐতিহাসিক স্তরে এসে, সমাজ বিভক্ত হয়ে গেছে শ্রেণীতে: সাধারণ মানুষ হয়েছে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের অধীন, মেয়েরা হয়েছে পুরুষের কর্তৃত্বের অধীন। অথচ শিকারি-সংগ্রাহকদের জীবনে এসব কিছুই অনুপস্থিত। শ্রেণী সমাজে প্রবেশ করার আগে প্রায় লক্ষাধিক বছর আমরা পৃথিবীতে টিকে থেকেছি একে অপরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করার মাধ্যমে সমতার ভিত্তিতে, যে প্রসঙ্গে নৃবিজ্ঞানী রিচার্ড লি বলছেন: " It is the long experience of egalitarian sharing that has moulded our past. Despite our seeming adaptation to life in hierarchical societies, and despite the rather dismal track record of human rights in many parts of the world, there are signs that humankind retain a deep rooted sense of egalitarianism, a deep rooted community to the norm of reciprocity, a deep rooted .... sense of community." [৩] (শেষ)
সূত্র ও সহায়ক পাঠ:
১) Origin of the Family, Private Property, and the State, Friedrich Engels (1891), Marxists internet archive; পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি, ফ্রেডরিক এঙ্গেলস, NBA, (2007)।
২) Engels and the Origins of Human Society, Chris Harman (1994).
৩) A People’s History of the World, Chris Harman, Orient Black Swan (2005).
৪) Introduction to Origin of the Family, Private Property and the State, by Frederick Engels, Eleanor Burke Leacock (1971).
৫) মার্ক্সবাদ ও ফ্রেডরিক এঙ্গেল্স―ফিরে দেখা, অশোক মুখোপাধ্যায়, বহুবচন (২০২০)।
৬) Myths of Male Dominance, Eleanor Burke Leacock, Haymarket Books Chicago, lllinois (1981).
৭) The Cambridge Encyclopedia of Hunters and Gatherers, Edited by Richard B. Lee and Richard Daly (1999).
৮) Man the hunter, Edited by Richard B. Lee and Irven DeVore with the assistance of Jill Nash-Mitchell, ALDINE DE GRUYTER / New York (1987).
৯) The Making of Mankind, Richard E. Leakey, E. P. DUTTON, NEW YORK (1981).
১০) NISA, The Life and Words of a !Kung Woman; Marjorie Shostak, Harvard University Press (1981).
১১) অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে, কার্ল মার্কস, মার্কস-এঙ্গেলস রচনা সংকলন, ভারবি (২০০০)।
১২) The Development of the Monist View of History, G.V. Plekhanov (1895), Marxists internet archive।

 By :
By :