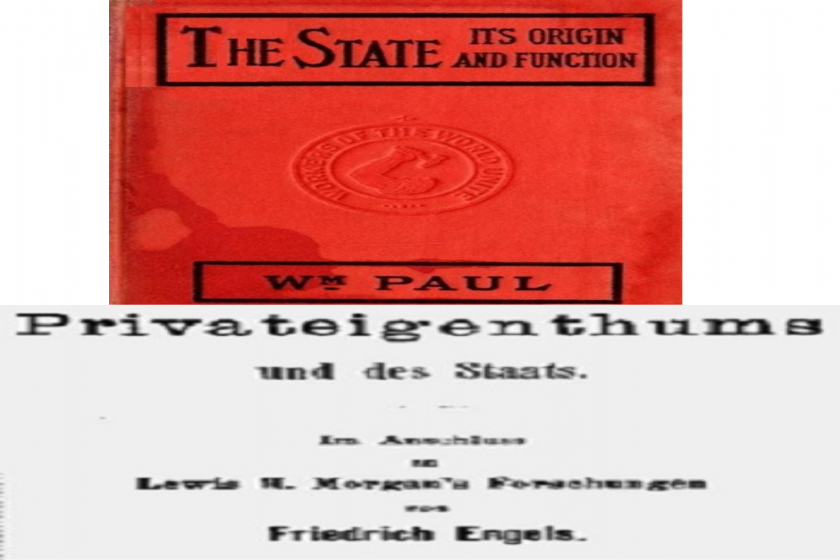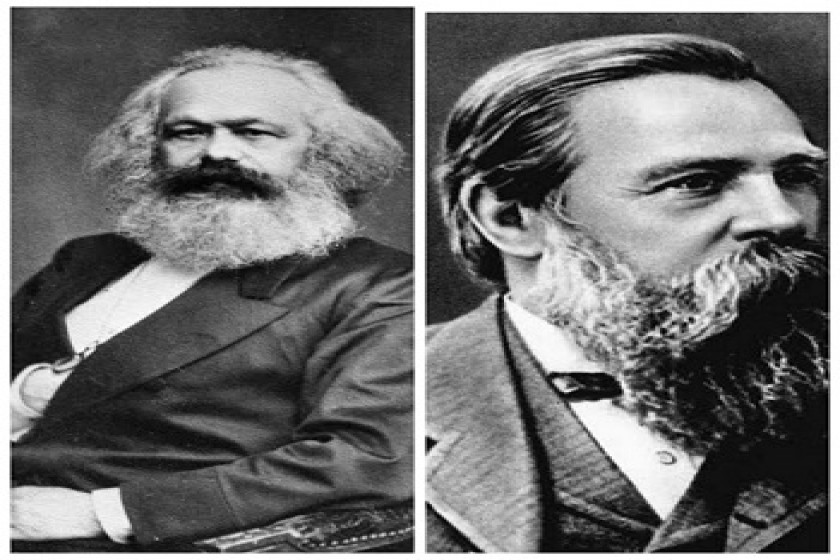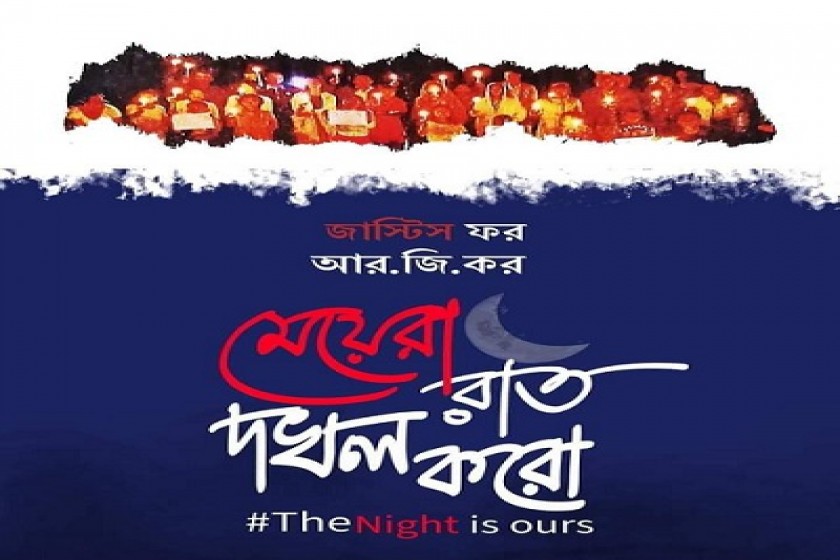শ্রেণি বিভাজন থেকে রাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিবর্তন
অশোক মুখোপাধ্যায়
মানব সমাজে আজ থেকে সাড়ে তিন থেকে আড়াই হাজার বছর আগে মিশর বা গ্রিসে ব্যক্তি সম্পত্তির উদ্ভবের মধ্য দিয়ে শ্রেণি বিভক্ত সমাজেরও আবির্ভাব হয়েছিল। সেই সব জায়গাতেই আমরা রাজা, রাজতন্ত্র ইত্যাদির প্রাথমিক স্তরের পরিচয় পাই। মিশরের ক্ষেত্রে ফারাওদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কিছু তথ্য উঠে এলেও রাষ্ট্র কাঠামোর বিষয়ে খুব বেশি কিছু এখনও জানা নেই। কিন্তু গ্রিস এবং রোমের শ্রেণি সমাজ ও দাস প্রথা ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া যায়। তার ভিত্তিতে এঙ্গেল্স তাঁর পরিবার ব্যক্তি সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি শীর্ষক গ্রন্থে রাষ্ট্রের উদ্ভব প্রসঙ্গেও বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাঁর সেই বিশ্লেষণ আজও প্রায় একশ শতাংশ অপরিহার্য হয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত রয়েছে। তাঁর সময়ে বিশ্বের প্রাচীন ইতিহাসের ব্যাপারে যতটুকু তথ্য জানা ছিল, প্রধানত ইউরোপের, এবং বিশেষ করে গ্রিস এবং রোম সম্পর্কে, তার ভিত্তিতেই তিনি রাষ্ট্রের উদ্ভবের সেই সুন্দর তথ্যচিত্র তুলে ধরেন। পরবর্তী কালে এর সাথে আরও কিছু নতুন তথ্য সংযোজিত হয়েছে, কিন্তু এঙ্গেল্সের মূল বক্তব্যকে পরিবর্তন করার দরকার পড়েনি। বরং বলা ভালো, তাঁর দেখানো পথেই এই ধরনের ঐতিহাসিক অনুসন্ধান এগিয়েছে।
[১]
এঙ্গেল্স দেখিয়েছেন, প্রাক-শ্রেণি গোষ্ঠী ভিত্তিক জনজাতি সমাজে বিভিন্ন মানব দলগুলির ভেতরেও এক ধরনের সামাজিক কর্তৃত্ব কাজ করত। এক একটা গোষ্ঠীর বয়স্ক এবং শক্তিমান সদস্যদের নিয়ে এক একটা সমিতি থাকত। সেই সমিতিগুলিই সামাজিক শিকার সংগ্রহ বা চাষের ব্যাপারে, পশুপাখির দেখভালের প্রশ্নে এবং নানা রকম উৎসব অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিত। আমাদের দেশে পুরুলিয়া বাঁকুড়া জেলার ক্ষেত্রে গ্রামীন সমাজে কয়েক দশক আগেও ষোল আনা নামে এক রকমের যৌথ সভা এবং আলোচনার ব্যবস্থা ছিল। একটা গ্রামের সমস্ত পরিবার থেকে একজন করে বয়স্ক ব্যক্তি এসে সেই ষোল আনার সভায় যোগ দিত। শ্রেণি বিভাজনের বহু কাল পরেও এরকম একটা প্রথার রেশ এখানে থেকে গিয়েছিল। এই সমস্ত সভার অ্যাজেন্ডা খুবই সীমিত হয়ে গেছে। তবু অন্তত গ্রামের নিজস্ব কিছু আচার আচরণের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার অস্তিত্ব থেকে বিগত দু হাজার আড়াই হাজার বছর আগেকার অবস্থা এবং ব্যবস্থা সম্পর্কে হয়ত কিছুটা আন্দাজ করা যায়।
সেই আদ্যিকালে এই জনজাতিগত সমিতিগুলির অধীনে বিচার্য বিষয়ের তালিকা ছিল বেশ লম্বা। চাষাবাদ কবে শুরু করা হবে, মাটিতে কবে লাঙল ফেলা হবে, কোন পশুদের কবে প্রজননের সময় এবং তার জন্য তাদের চরাতে নিয়ে যেতে হবে, কার কার কবে বিয়ে হবে, কারও সন্তান হলে তাকে কীভাবে এবং কবে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তির অনুষ্ঠান করতে হবে, কোন সময়ে কোন পশু শিকার করা যাবে এবং/অথবা যাবে না, কখন নদীতে হ্রদে বিলে মাছ ধরতে যাওয়া যাবে এবং/অথবা যাবে না, কোন পাশের গোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে এবং কবে, তাতে গ্রামের সদস্যদের কার কী ভূমিকা থাকবে — এরকম অনেক কিছু তারা এক সঙ্গে বসে ঠিক করত। তার ভিত্তিতে ক্রিয়া করত। কারও পক্ষেই সেই সিদ্ধান্তের কোনোটাই লঙ্ঘন করা সম্ভব হত না, এমনকি ইচ্ছাও হত না।
এই সমিতিগুলির গঠন হত কেবল মাত্র রক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে সংযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিনিময় যেমন যেমন বৃদ্ধি পেতে থাকে, ততই এক একটা গোষ্ঠীর সীমানায় অন্য গোষ্ঠী থেকে আগত বিনিময়কারীর সংখ্যাও বেড়ে যায়। এক দিকে যেমন গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে পণ্য বিনিময় তথা লোক চলাচল বৃদ্ধি পেতে থাকে, অন্য দিকে নানা প্রয়োজনে বাইরে থেকে আসা লোকজনের থেকে যাওয়া — প্রথমে অস্থায়ীভাবে, পরে ক্রমে ক্রমে স্থায়ীভাবেও — একটা স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়। সঙ্ঘর্ষের পাশাপাশি বাস্তব অর্থনৈতিক বিকাশক্রমের চাপেই এটা ঘটতে শুরু করে। এদের মধ্যে যারা একটু বেশি মাত্রায় সম্পদশালী তারা সমিতিতেও ঢোকার ছাড়পত্র পেয়ে যায়। রক্ত সম্পর্কিত সদস্য ভিত্তিক সমিতি ধীরে ধীরে তার জনজাতিগত চরিত্র হারিয়ে আঞ্চলিক গঠন অর্জন করে ফেলতে থাকে।
এদিকে সেই প্রাচীন কৃষি ও পশুপালন ভিত্তিক সমাজে যখন শ্রম বিভাজন ঘটেছে, তার ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রম দল তথা পরিবারের হাতে তাদের জন্য নির্ধারিত কর্মভাগ অনুযায়ী স্বতন্ত্র হাতিয়ার সমূহ জমা হয়ে চলেছে, তারই পরিণতিতে আরও একটা ঘটনা জায়গা করে নেয়। এমনিতে কাছাকাছি থাকা মানব দলগুলির মধ্যে পারস্পরিক সঙ্ঘর্ষ লেগেই থাকত। কেন না, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ খাদ্যের উৎস প্রকৃতিতে যত অঢেলই হোক, তা কখনই সমস্ত মানব গোষ্ঠীর সমস্ত সদস্যদের জন্য যথেষ্ট হত না। তাই বড় বড় পশু শিকার এবং পার্শ্ববর্তী মানব গোষ্ঠীর সঙ্গে সঙ্ঘর্ষের জন্য শ্রম বিভাজনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই প্রতিটি মানব দলের ভেতরে অস্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এক দল নিপুণ অস্ত্রধারী বাহিনী তৈরি হয়। তুলনামূলক অর্থে যাদের বয়স কম, পরিশ্রমী, সাহসী, পেশীশক্তিতে বলীয়ান, হাতিয়ার ব্যবহারে দক্ষ, তৎপর এবং ক্ষিপ্র, যাদের চোখের নজর তীক্ষ্ণ — তাদের নিয়েই এই বাহিনী গঠিত হতে থাকে। তখনকার রেওয়াজ অনুযায়ী পশু শিকারে এবং যুদ্ধ সঙ্ঘর্ষে একটা গোষ্ঠীর সমস্ত সদস্যই অংশগ্রহণ করত, কিন্তু এই বিশেষ বাহিনীর উপর দায়িত্ব পড়ত সামনে থেকে লড়াই পরিচালনা করার — আক্রমণ ও আত্মরক্ষার সমস্ত দায়িত্ব পালন করার। তবে তখনও তারা গোষ্ঠীর যৌথ সমিতির অধীনে থেকেই তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করত।
ব্যক্তি সম্পত্তি উদ্ভবের পরে যখন থেকে এই বিষয়টা ক্রমাগত একটা স্থায়ী কাঠামো অর্জন করতে থাকে, তখন সম্পত্তিবানদের তরফে এই কাঠামোকে রক্ষা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রথমে আশেপাশের তুলনামূলক অর্থে কম সম্পদশালী জনগোষ্ঠীর হাত থেকে। কেন না, জনজাতি ভিত্তিক সমাজে যে গোষ্ঠীগত সঙ্ঘর্ষ বরাবরই চালু ছিল, এই সম্পদের তারতম্যকে কেন্দ্র করে তার সম্ভাবনা স্বভাবতই আরও বেড়ে যায়। আবার দ্বিতীয়ত, একই গোষ্ঠীর মধ্যেও তুলনামূলক অর্থে যারা গরিব তাদের তরফ থেকে আক্রমণের এবং লুটপাটের সম্ভাবনা বাড়তে থাকে, মাঝে মাঝে ঘটতেও থাকে। কেন না, একবার অস্ত্রের সাহায্যে অন্য গোষ্ঠীর সম্পদ লুটে আনা চালু হয়ে যাওয়ার পর সেটা নিজ গোষ্ঠীর ভেতরেও প্রয়োগ শুধু সময়ের অপেক্ষা।
উপরে আমরা যে বিশেষ ভাবে নিপুণ সশস্ত্র বাহিনীর কথা উল্লেখ করেছি, সমিতিগুলির উপর প্রভাব খাটিয়ে সম্পত্তিবানদের তরফে গোষ্ঠীতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার নামে সেই বাহিনীকে এই কাজে নিয়োগ করার চেষ্টা শুরু হয়। এই সশস্ত্র মানব দলের ভেতর থেকেই প্রথম এক ধরনের ভ্রূণ-রাষ্ট্র (protostate)-এর জন্ম হয়। এটাকে আমরা ভ্রূণ বলছি — কেন না, তখনও তার মধ্যে শ্রেণি রাষ্ট্রের সমস্ত বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠেনি।
শ্রেণি বিভাজনের মধ্য দিয়ে যখন দাস প্রথা পুরোদস্তুর চালু হয়ে গেল, এবং সমস্ত উৎপাদন ও সামাজিক কাজকর্ম গোষ্ঠীভুক্ত ও গোষ্ঠী বহির্ভূত দাস মজুরদের দিয়ে করানো চলতে লাগল, এর একটা অন্যতম অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ছিল, গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পত্তিহীন দুঃস্থ জনসাধারণের এক বৃহত্তর অংশ সম্পূর্ণ কর্মহীন বেকারে পর্যবসিত হল। তাদের হাতে না আছে কোনো কাজ, না আছে খাদ্য বস্ত্র সংগ্রহের সুযোগ। ফলে তাদের মধ্যে যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছিল, নতুন এই সমাজকে তাকেও সামলানোর কথা ভাবতে হল। এথেন্স-এর রাষ্ট্র গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ইংল্যান্ডের এক শ্রমিক নেতা উইলিয়াম পল ১৯১৭ সালে রচিত এক গ্রন্থে লিখেছিলেন: “Thus, within Athens, there grew an expanding army of slaves who gradually deprived freemen of their livelihood. Those unemployed wretches were the source of many agitations. During grave crises, these propertyless workers set up a demand for return to the old communism. . . . Under pericles this problem became so serious that, by means of small State jobs, he provided a living for the destitute free labourers, who were gradually transformed into a band of parasites.” [Paul 2012, 57] তার থেকেই সশস্ত্র বাহিনীর পাশাপাশি আরও একটা বিশেষ অনস্ত্র নাগরিক বাহিনী তৈরি করা হল, যারা বিভিন্ন সামাজিক কাজের দায়িত্ব বন্টন করবে, সাধারণ নাগরিকদের থেকে কর আদায় করবে, এই সবের দাপ্তরিক হিসাব রাখবে, ইত্যাদি। এইভাবে ধাপে ধাপে এক সময় এক একটা অঞ্চল ও গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ইতি মধ্যে গড়ে ওঠা ভ্রূণ-রাষ্ট্র ব্যবস্থা একটা পূর্ণ বিকশিত রাষ্ট্র কাঠামোয় পর্যবসিত হল।
[২]
এই প্রক্রিয়া বোঝাতে চেয়েই এঙ্গেল্স বলেছিলেন, "In this manner, the organs of the gentile constitution were gradually torn from their roots in the people, in gens, phratry and tribe, and the whole gentile order was transformed into its opposite: from an organization of tribes for the free administration of their own affairs, it became an organization for plundering and oppressing their neighbours; and correspondingly, its organs were transformed from instruments of the will of the people into independent organs for ruling and oppressing their own people." [Engels]
প্রথমে তিনি বেছে নিয়েছেন গ্রিসের ইতিহাস। ব্যক্তি সম্পত্তির উদ্ভবের সাথে সাথে ধীরে ধীরে প্রাচীন জনজাতীয় রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এবং টিকে থাকা সমাজ সংগঠনের ভেতরে ভাঙন ধরতে থাকে এবং বহুজাতিক ও আঞ্চলিক নতুন ধরনের এক সামাজিক অস্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে: “এভাবে আমরা বীরযুগের গ্রিকদের সংবিধানে প্রাচীন গোত্র সংগঠনের পূর্ণোদ্যম অস্তিত্ব লক্ষ করি; কিন্তু তার বিলুপ্তির সূত্রপাতও সহজদৃষ্ট। পিতৃ-অধিকার এবং সন্তানসন্ততি কর্তৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার, যা পারিবারিক সম্পদ সঞ্চয়ে সাহায্য করেছে এবং পরিবারকে গোত্রের বিরোধী শক্তিতে পরিণত করেছে; ধনের অসমতা বংশানুক্রমিক অভিজাতকুল ও রাজতন্ত্রের ভ্রূণাঙ্কুর সৃষ্টিক্রমে সামাজিক ব্যবস্থার উপর ফিরতি প্রভাব বিস্তার করল; যে দাসপ্রথা প্রথমে যুদ্ধবন্দিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তা ইতিমধ্যেই উপজাতির অন্যান্য ব্যক্তি, এমনকি স্বগোত্রজদেরও দাসত্ব বন্ধনের পথ প্রশস্ত করছিল; প্রাচীন আন্তঃউপজাতীয় যুদ্ধ অতঃপর জীবিকা নির্বাহের জন্য গবাদি পশু, দাস ও সম্পদ জলেস্থলে লুণ্ঠনের নিয়মিত হামলায় অধঃপতিত হয়েছিল; সংক্ষেপে—ধনের প্রশস্তি, তাকেই শ্রেষ্ঠ কল্যাণ বলে সম্মান প্রদর্শন এবং বলপূর্বক ধন লুণ্ঠনের জন্য গোত্রের সাবেকি বিধিবিধানকে বিকৃত করা হল। কেবলমাত্র একটি জিনিসের তখনও অভাব ছিলঃ একটি সংস্থা যা নবলব্ধ ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে গোত্রব্যবস্থার সাম্যতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে থেকে বাঁচাবে তাই নয়, এত দিন যাকে হেয় জ্ঞান করা হত সেই ব্যক্তিগত মালিকানাকে পবিত্র করবে, সেই পবিত্রকরণকে মানব সমাজের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য বলে ঘোষণা করবে এবং এবং শুধু তাই নয়, অধিকন্তু সম্পত্তি আহরণের একটার পর একটা বিকাশমান নতুন রূপগুলির উপর ও ফলত দ্রুত বর্ধমান ধন সঞ্চয়ের উপর সাধারণ সামাজিক অনুমোদন মুদ্রিত করবে; এমন একটি সংস্থা যা সমাজের উদীয়মান শ্রেণিবিভাগই শুধু নয়, পরন্তু বিত্তবান শ্রেণি কর্তৃক বিত্তহীন শ্রেণিগুলিকে শোষণ করার অধিকার, বিত্তহীনদের উপর বিত্তবানদের শাসনও চিরস্থায়ী করবে।
এবং সে সংস্থা এল। উদ্ভাবিত হল রাষ্ট্র।” [Engels 1968, 106-07; italics in the original]
এই রাষ্ট্র যখন এল, সে পুরনো সমাজ পরিচালন পদ্ধতিকে আমূল বদলে দিল। পারস্পরিক আলোচনা ঝগড়াবিবাদ ও অবশেষে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহনের দীর্ঘ দিনের রেওয়াজের বদলে এসে গেল মুষ্টিমেয় পরাক্রমশালী সম্পত্তিবান ও ক্ষমতাবান লোকেদের গৃহীত সিদ্ধান্ত বাকিদের মেনে নেবার এবং মানিয়ে নেবার পদ্ধতি। মর্গ্যান দেখালেন পরিবর্তনের স্পষ্ট চিহ্নগুলো। এঙ্গেল্স দেখালেন তার পেছনে ক্রিয়াশীল আর্থসামাজিক ঐতিহাসিক কারণসমূহের ভূমিকা:
“How the state developed, some of the organs of the gentile constitution being transformed, some displaced, by the intrusion of new organs, and, finally, all superseded by real governmental authorities—while the place of the actual “people in arms” defending itself through its gentes, phratries and tribes, was taken by an armed “public power” at the service of these authorities and, therefore, also available against the people—all this can nowhere be traced better, at least in its initial stage, than in ancient Athens. The forms of the changes are, in the main, described by Morgan; the economic content which gave rise to them I had largely to add myself.” [Engels 1968, 107]
ঠিক প্রায় একই প্রক্রিয়া লক্ষ করা যায় রোমান রাষ্ট্র গড়ে ওঠার ক্ষেত্রেও।
“বীরযুগের গ্রিকদের মতোই তথাকথিত রাজাদের সময়কার রোমানরা গোত্র ফ্রাত্রি ও উপজাতি ভিত্তিক একটি সামরিক গণতন্ত্রে বাস করত, যা থেকে এর বিকাশ ঘটে। যদিও কিউরিয়া ও উপজাতিগুলি অংশত কৃত্রিমভাবে সংগঠিত হয়েও থাকে, তবু যে সমাজে তাদের উদ্ভব এবং যাতে তখনও তারা চারদিকে বেষ্টিত, সেই সমাজেরই খাঁটি ও স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত আদর্শের ছাঁচেই তাদের গড়া হয়েছিল। যদিও স্বতস্ফূর্তভাবে বিকশিত আশরাফ অভিজাতরা ইতিমধ্যেই তাদের অটল পদ্ভূমির আশ্রয় লাভ করেছিল, এবং রেক্সরা ক্রমে ক্রমে তাদের অধিকার বৃদ্ধিতে সচেষ্ট ছিল, তবুও এতে শাসন ব্যবস্থার আদি মৌলিক চরিত্র বদলে যায় না এবং এটাই আসল কথা।
ইতিমধ্যে রোম নগরী ও দেশজয়ের ফলে প্রসারিত রোম প্রদেশের জনসংখ্যা অংশত বহিরাগতদের জন্য এবং অংশত বিজিত অঞ্চলগুলি, বিশেষত লাতিন জেলেগুলির জনগণ মারফত বাড়তে থাকে। এসব নতুন প্রজারা (এখনকার মতো আমরা আশ্রয়াধীন্দের কথা আলোচনা করছি না) পুরাতন গোত্র, কিউরিয়া ও উপজাতির বাইরের লোক এবং সেজন্য এরা পপুলুস রোমানুস বা যথার্থ রোমান জাতির অন্তর্গত নয়। এরা ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন ছিল, এরা জমির মালিক হতে পারত, এদের খাজনা দিতে হত এবং যুদ্ধের কাজ করারও দায়িত্ব ছিল। কিন্তু তারা সরকারি পদ পেতে এবং কিউরিয়াগুলির সভায় অংশ নিতে কিংবা বিজিত রাষ্ট্রের ভূমিবন্টনেরও অংশভাগী হতে পারত না। তারাই সমস্ত রাষ্ট্রীয় অধিকার বঞ্চিত আতরাফ। অবিরাম সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সামরিক শিক্ষা ও অস্ত্রসজ্জার জন্য তারা পুরাতন পপুলুসের কাছে — এখন বহিরাগতদের নিয়ে যাদের সংখ্যাবৃদ্ধির সমস্ত পথ কঠোরভাবে বন্ধ করা হয়েছিল — ত্রাসের কারণ হয়ে উঠল। উপরন্তু মনে হয়, পপুলুস ও আতরাফদের মধ্যে জমির মালিকানা এক রকম সমভাবেই বন্টন করা হয়েছিল, কিন্তু বাণিজ্য ও শিল্পজাত সম্পদ তখনও তত প্রচুর না হলেও প্রধানত তা আতরাফদের হাতেই ছিল।
একেই তো রোমের ঐতিহাসিক সূচনাপর্বের কিংবদন্তিগত উৎপত্তির সবই ঘন অন্ধকারে আবৃত; তার উপর আবার তাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে সমস্ত যুক্তিনিষ্ঠ প্রয়োগবাদী চেষ্টা হয়েছে এবং পরবর্তীকালে আইনি শিক্ষাপ্রাপ্ত লেখকরা আমাদের কাছে মূল গ্রন্থ স্বরূপ যে সমস্ত রচনা রেখে গেছেন, তার ফলে এই অন্ধকার আরও ঘনীভূত হয়েছে; এই কারণেই কখন, কোন পথে, কী কী কারণে বিপ্লব এসে পুরনো গোত্র প্রথার অবসান ঘটিয়েছিল সেসম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট বক্তব্য উপস্থিত করা অসম্ভব। তবে আতরাফ এবং পপুলুসের মধ্যেকার সঙ্ঘর্শের ভেতরেই যে এই সমস্ত কারণ নিহিত সে সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত।
রেক্স সার্ভিয়ুস তুলিয়ুসের নামে প্রচলিত শাসনতন্ত্র অনেকটা গ্রিক ধাঁচের, বিশেষত সলোনের শাসনতন্ত্রের ঘনিষ্ট; এর সৃষ্ট নতুন জনসভায় আশরাফ ও আতরাফ শুধু সামরিক দায়িত্ব পালন করে কিনা এই নিরিখেই সমভাবে তার অন্তর্ভুক্ত হল অথবা বাদ পড়ল। সামরিক দায়িত্ব পালনে বাধ্য সমস্ত পুরুষ জনসংখ্যাকে সম্পত্তি অনুযায়ী ছয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা হল। . . .
এই নবগঠিত সেন্টুরিয়ার উপর সে সব রাজনৈতিক অধিকার অর্সাল, যা পূর্বতন কিউরিয়া সভার হাতে ছিল (নাম মাত্র কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া); এর ফলে এথেন্সের মতো এখানেও কিউরিয়া ও এগুলির অন্তর্ভুক্ত গোত্রগুলি অধঃপতিত হয়ে কেবল ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় সংগঠনে পর্যবসিত অবস্থায় সেভাবে বহুদিন টিকেছিল, কিন্তু কিউরিয়া সভার অচিরেই বিলোপ ঘটল। তিনটি পুরনো গোত্র ভিত্তিক উপজাতিকেও রাষ্ট্র থেকে অপসারণের জন্য চারটি অঞ্চল ভিত্তিক উপজাতি গঠন করা হল — এরা নগরের এক একটি পাড়ায় বাস করত এবং কিছু রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করত।
এভাবে রোমেও ব্যক্তিগত রক্তবন্ধনের ভিত্তিতে পুরাতন সামাজিক ব্যবস্থা তথাকথিত রাজপ্রথা অবসানের আগেই ধ্বংস হয়ে গেল এবং আঞ্চলিক বিভাগ ও সম্পত্তির তারতম্যের ভিত্তিতে একটি নতুন রীতিমতো রাষ্ট্রব্যবস্থা তার স্থলবর্তী হল। এখানে সৈন্যদলে বাধ্যতামূলকভাবে কর্মরত নাগরিকদের হাতেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল এবং এই ক্ষমতা শুধু দাসদের বিরুদ্ধেই নয়, সামরিক দায়িত্ব ও অস্ত্র বহনের অধিকার বঞ্চিত তথাকথিত প্রলেতারীয়দের বিরুদ্ধেও প্রযুক্ত হত।” [Engels 1968, 126-28]
এর পর তিনি আয়ার্ল্যান্ড এবং জার্মানিতে প্রাচীন কালের জনজাতীয় সমাজ থেকে রাষ্ট্রীয় সংগঠন গড়ে ওঠার ইতিহাসের উপরও কিছুটা আলোকপাত করেন। এই ভাবে এই বইটি ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার এক চির-অনুসরণীয় ধ্রুপদী দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে। আপন বিশ্বাস মতবাদ বা ধারণাকে জবরদস্তি ইতিহাসের উপর চাপিয়ে দেওয়া নয়, বাস্তব তথ্য বিশ্লেষণ করতে করতে তার মধ্য থেকে যতদূর সম্ভব সমাজ বিকাশের নিয়মগুলিকে স্পষ্ট করে চিনিয়ে দেওয়া — এই হল এই ধ্রুপদী মার্ক্সীয় গ্রন্থটির উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য।
[৩]
এই আলোচনার মধ্য দিয়েই তিনি পাঠককে সতর্ক করেন এই বলে যে রাষ্ট্র কোনো শ্রেণি নিরপেক্ষ উদার সামাজিক হাতিয়ার নয়। শ্রেণি বিভক্ত সমাজের আবির্ভাবের সঙ্গেই এরও আবির্ভাব। “The state is, therefore, by no means a power forced on society from without; just as little is it “the reality of the ethical idea”, “the image and reality of reason”, as Hegel maintains. [Vide Hegel’s Philosophy of Law; Arts. 257; p. 360 — A. M.] Rather, it is a product of society at a certain stage of development; it is the admission that this society has become entangled in an insoluble contradiction with itself, that it has split into irreconcilable antagonisms which it is powerless to dispel.” [Engels 1968, 166]
এঙ্গেল্স আরও বলেন, “যেহেতু শ্রেণিবিরোধকে সংযত করবার প্রয়োজন থেকেই রাষ্ট্রের উদ্ভব, এবং যেহেতু এটি ঐ সংঘর্ষের মধ্যেই উৎপন্ন, সেজন্য এটি সাধারণত সবচেয়ে পরাক্রমশালী ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রভুত্বকারী শ্রেণির রাষ্ট্র, যারা রাষ্ট্রের মাধ্যমে রাজনীতির ক্ষেত্রেও আধিপত্যকারী শ্রেণি হয়ে ওঠে এবং ফলত নিপীড়িত শ্রেণির দমন এবং তার শোষণে নতুন হাতিয়ার লাভ করে। . . . ইতিহাসে জ্ঞাত অধিকাংশ রাষ্ট্রেই দেখা যায় যে, নাগরিকদের অধিকার ধন সম্পত্তির অনুপাতে নির্ণীত এবং এতে রাষ্ট্র যে বিত্তহীন শ্রেণির বিরুদ্ধে বিত্তশালী শ্রেণির একটি আত্মরক্ষামূলক সংগঠন তা প্রত্যক্ষভাবে প্রকটিত হয়।” [Engels 1968, 168-69]
তাই তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত: “অতএব রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অনন্তকালীন নয়। এমন সমাজ ছিল যা রাষ্ট্র ছাড়াই চলত, যার রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রীয় ক্কমতার কোনো ধারনাই ছিল না। অর্থনৈতিক বিকাশের একটি বিশেষ স্তরে যখন সমাজে শ্রেণিবিভাগ অবধারিত, তখন এই বিভাগের জন্যই রাষ্ট্র অপরিহার্য হয়ে পড়ল। এখন আমরা দ্রুত উতপাদন বিকাশের এমন একটি স্তরে পৌঁছচ্ছি যখন এসব শ্রেণির অস্তিত্ব শুধু যে অপরিহার্য থাকবে না তাই নয়, উপরন্তু এরা উতপাদনের প্রত্যক্ষ প্রতিবন্ধ হয়েই উঠবে। পূর্ববর্তী স্তরে যেমন অনিবার্যভাবে শ্রেণিসমূহের উদ্ভব হয়েছিল, তেমনই এগুলির অনিবার্য পতন ঘটবে এবং পতন ঘটবে এগুলির আনুষঙ্গিক রাষ্ট্রেরও। উৎপাদকদের স্বাধীন ও সমান সম্মিলনের ভিত্তিতে যে সমাজ উৎপাদনকে পুনর্গঠিত করবে, সে সমাজ সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে পাঠাবে তার যোগ্য স্থানে; পুরা দ্রব্য সংগ্রহশালায়, চরকা ও ব্রোঞ্জ কুড়ুলের পাশে।” [Engels 1968, 170]
এই সব জরুরি কথা আজকের দিনের নৈমিত্তিক কাজের ভিড়ে ভুলে গেলে চলবে না।
সব শেষে, এই প্রসঙ্গে একজন প্রখ্যাত ব্রিটিশ মার্ক্সবাদী বিশ্লেষক ক্রিস হারম্যানের একটি মন্তব্যের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে: বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একশ বছরের একটি পুরনো সমীক্ষা সচরাচর খুব একটা চর্চার বিষয় হয়ে থাকে না, নতুনতর গবেষণা ও প্রাপ্ত তথ্যের নিরিখে সহজেই অপ্রচলিত হয়ে যায়। এঙ্গেল্সের এই বইটির ক্ষেত্রে কিন্তু তা হল না। অনেক কিছুই হয়ত বাতিল হয়ে যাবে, নতুন করে অনেক কিছুই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে হবে। কিন্তু তারপরও যা থেকে যাবে তার পরিমাণ উপেক্ষনীয় নয়। “It is an enormous credit to Engels and to the method that he and Marx developed in the mid-1840s that they still provide us with insights which are lacking in so many present day writings on the evolution of our species and of society. They contain much which has to be discarded or rejigged on the basis of what had been discovered since Engels died. But what remains is still of immense value. It forms an invaluable starting point for anyone who wants to make sense of the mass of empirical material produced on an almost daily basis by archaeologists and anthropologists.” [Harman 1994]
[৪]
মার্ক্সবাদের বিচারে রাষ্ট্র গঠনের পেছনে আছে দুটি মৌল নীতি: ক) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, খ) সার্বিক কর্তৃত্ব। জনৈক সোভিয়েত লেখকের ভাষায়, “The state has two basic characteristics. The first is the territorial principle of organization of the population and its relation to the social authority; the second is the existence of the public authority, i.e., a social authority that is not immediately identical with the entire population.” [Selezniyov 1968, 161-62]
ব্যাখ্যা করা যাক।
প্রতিটি রাষ্ট্রের একটা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখা আছে। সেই সীমানার মধ্যে সেই রাষ্ট্রই রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, ভাষা, ইত্যাদি সমস্ত কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকারী এবং অন্য কোনো রাষ্ট্র তার মধ্যে নাক গলাতে পারবে না। এটাকে বলা হয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব (sovereignty) বা সার্বভৌম ক্ষমতা (sovereign power)। আন্তর্জাতিক আইন রীতিনীতি ও উপলব্ধি অনুযায়ী প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্যই অপর প্রতিটি রাষ্ট্রের এই সার্বভৌমত্ব অলঙ্ঘনীয়। যদিও শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি প্রায়শই দুর্বলতর রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই নীতি অনায়াসে নির্লজ্জ ভাবে যখন খুশি লঙ্ঘন করে থাকে।
একটি আধুনিক রাষ্ট্র তো বটেই, এমনকি প্রাচীন দাস যুগের রাষ্ট্র বা সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রও তার ক্ষমতাধীন এলাকাকে কিছু কিছু ছোট অন্তর্বর্তী এলাকায় ভাগ করে নিত। প্রদেশ, জেলা, পরগণা, তালুক, মৌজা, ইত্যাদি। এক একটা ছোট ভাগের জন্য এক একজন করে শাসন কর্তা নিয়োগ করা হত। এই ভাগাভাগির জন্য কোনো ট্রাইব্যাল সম্পর্ক বা রক্তের সম্পর্ক দেখা হয় না। বুর্জোয়া রাষ্ট্রে এই ভাগগুলিতে শাসন করার জন্যও কিছু নির্বাচিত কাঠামো রাখা হয়। পঞ্চায়েত, পুরসভা, ইত্যাদির আকারে। এই নিম্নস্তরের নামে গণতন্ত্র প্রশাসনিক দিক থেকে বিকেন্দ্রীকরণ হলেও আসলে শাসক গোষ্ঠীর পক্ষে তার শাসনের জাল একেবারে গ্রাম স্তর পর্যন্ত বিস্তার করে দেওয়া হয়। নামে যতই গণতন্ত্রের প্রসারণ বলে হইচই করা হোক না কেন, আসলে রাষ্ট্র এইভাবে রাজধানীর বক্ষস্থল থেকে একেবারে প্রত্যন্ত গ্রামের পুকুরের পারে অবধি পৌঁছে যায়। আর ঠিক এই ঘটনার তাৎপর্য আজকাল অনেক মার্ক্সবাদীও ভুলে গিয়ে অথবা দেখতে না পেরে একে বেশ খানিক প্রশংসা ছলে তৃণমূল স্তরের গণতন্ত্র বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন।
দ্বিতীয়ত, যে কোনো রাষ্ট্রের অপর বৈশিষ্ট্যটি হল বৃহত্তর জনগণের উপর এক অতি ক্ষুদ্রাংশের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব। দাস প্রথা ভিত্তিক বা সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের এই কর্তৃত্ব স্থাপিত হত প্রধানত ধর্ম এবং/অথবা ঈশ্বরের নামে। রাজা বাদশাহদের মনে করা হত, এমনকি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে প্রচারও করা হত, ঈশ্বর আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে। পক্ষান্তরে, আধুনিক কালের বুর্জোয়া রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব নির্মিত হয় আইনের নামে। অথবা সংবিধানের নামে। একটা রাষ্ট্রের সংবিধান হল আইনের সর্বোচ্চ ঘনীভূত রূপ। নাগরিক সমাজকে এই আইন সংবিধান ইত্যাদি মেনে চলতে হয়। পুলিশ প্রশাসন আইন আদালত ইত্যাদি রয়েছে আইন লঙ্ঘনকারীদের শাস্তিবিধানের নিয়মানুগ ব্যবস্থা হিসাবে। মার্ক্সবাদে রাষ্ট্রের এই কর্তৃত্বকে ব্যাখ্যা করা হয় শ্রেণির একনায়কত্ব (dictatorship of a class) হিসাবে। বুর্জোয়া গণতন্ত্র হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়া শ্রেণির একনায়কত্ব।
সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রও এই বৈশিষ্ট্যগুলির অধিকাংশই ধারণ করে। প্রথমত, সেই রাষ্ট্রও স্থাপিত হয় একটা জাতীয় ভূখণ্ডের উপরে। সেই নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের উপর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব বা সার্বভৌমত্ব বহাল থাকে। দুটি পাশাপাশি অবস্থানে থাকা সমাজতান্ত্রিক দেশও পরস্পরের এই ভৌগোলিক অখণ্ডতাকে সম্মান করে; শক্তিশালী রাষ্ট্র হলে দুর্বল রাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকারকে লঙ্ঘন করে না। আসলে করার কথা নয়। কিন্তু অতীতে হাঙ্গেরি ও চেকশ্লোভাকিয়ায় সোভিয়েত রাশিয়ার সেনা হস্তক্ষেপ, সোভিয়েত চিনের মধ্যে যুদ্ধ, কাম্পুচিয়ায় ভিয়েতনামের আগ্রাসন, চিনের সঙ্গে ভিয়েতনামের যুদ্ধ ইত্যাদি ঘটনাগুলি দেখিয়ে দিয়েছে, নানা রকম আদর্শগত অধঃপতনের ফলে এই সমস্যাগুলির অভ্যুদয় সম্ভব। আবার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাঠামোতেও আঞ্চলিক বিভাজন থাকে এবং এক একটা পর্যায়ের অঞ্চলের জন্য সোভিয়েত বা কমিউন জাতীয় প্রশাসনিক কাঠামো নির্মিত হয়। এখানেও শাসনতন্ত্রের দিক থেকে বিকেন্দ্রীকরণ করা হলেও এই সমস্ত কাঠামোর মধ্য দিয়ে একটা কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কাজ করতে থাকে।
তাছাড়া, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও জনগণের এক অংশ অপর অংশের উপরে কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে। সেই কারণে কোনো রকম ঢাক ঢাক গুড় গুড় না করে, কথার মারপ্যাঁচে না গিয়ে মার্ক্স একে সরাসরি সর্বহারার একনায়কত্ব (dictatorship of the proletariat) হিসাবেই চিহ্নিত করেছেন। এই রাষ্ট্রেও অভ্যন্তরীন শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ এবং সীমান্ত রক্ষা ও নানা রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় জনগণকে সাহায্য করার স্বার্থে স্থায়ী সেনাবাহিনী থাকে এবং থাকবে। এখানেও বিচার ব্যবস্থা এবং কারাগার বজায় থাকবে। সমাজতন্ত্রেও দৈনন্দিন রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম পরিচালনার জন্য একটা পূর্ণাঙ্গ প্রশাসন যন্ত্র থাকবে। কমিউনিস্টদের মধ্যে এক সময় আমলাতন্ত্র বিরোধিতা জাত এক ধরনের ইউটোপিয়া ছিল, বিপ্লবের পর সমাজতন্ত্র স্থাপিত হলেই বুর্জোয়া রাষ্ট্রের এই সব আপদ দূর করে ফেলা যাবে। পারি কমিউনের সাফল্য ও ব্যর্থতা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মার্ক্স এঙ্গেল্সও এর বাইরে ছিলেন না। তাঁরাও বলেছিলেন যে কমিউন দেখিয়ে দিয়েছে, প্রশাসনিক আধিকারিকদের কীভাবে শ্রমিক শ্রেণির অধীনে নির্বাচন করে আনা হবে এবং উচ্চ হারের বেতনের বদলে সাধারণ শ্রমিকের প্রাপ্য মজুরির চাইতে বেশি বেতন দেওয়া হবে না। এমনকি রুশ বিপ্লবের ঠিক পূর্বক্ষণে লেখা রাষ্ট্র ও বিপ্লব বইতে লেনিনও ঘোষণা করেছিলেন যে সমাজতন্ত্রে সমস্ত প্রশাসনিক আধিকারিকদের নির্বাচিত হতে হবে, কেউই স্থায়ী কর্মী হিসাবে থাকতে পারবে না। উপরন্তু কাজকর্ম পছন্দ না হলে তাদের যে কোনো সময় পদ প্রত্যাহার করে নেবার অধিকার (right to recall) শ্রমজীবী জনগণের থাকবে। “All officials, without exception, elected and subject to recall at any time, their salaries reduced to the level of ordinary “workman's wages” — these simple and “self-evident” democratic measures, while completely uniting the interests of the workers and the majority of the peasants, at the same time serve as a bridge leading from capitalism to socialism. These measures concern the reorganisation of the state, the purely political reorganisation of society; but, of course, they acquire their full meaning and significance only in connection with the “expropriation of the expropriators” either being accomplished or in preparation, i.e., with the transformation of capitalist private ownership of the means of production into social ownership.” [Lenin 1974, 426] এরকম হলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আর একটা শক্তপোক্ত আমলাতন্ত্র গড়ে উঠতে পারবে না।
লেনিনের এই রচনায় এই প্রসঙ্গটি মার্ক্স এঙ্গেল্সের উদ্ধৃতি সহ ব্যাপক বিস্তারে আলোচনা করা হয়েছিল। কিন্তু বিপ্লবের পর সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের কাজে হাত দিয়ে খুব অল্প দিনের মধ্যেই লেনিন বুঝলেন, প্রশাসনিক কর্মীদের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচনে সংগ্রহ করে আনলে সরকারি জরুরি কাজকর্ম সব শিকেয় উঠবে। প্রশিক্ষিত অভিজ্ঞ ও স্থায়ী কর্মীই লাগবে প্রশাসনের নানা স্তরে। তারপর আর তিনি সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেননি। বরং বারবার দলের নেতাকর্মীদের বুঝিয়েছেন, এমনকি জারতন্ত্র ও কেরেনস্কি আমলের কর্মচারীদেরও উপযুক্ত ট্রেনিং দিয়ে এবং আদর্শগতভাবে উদ্বুদ্ধ করে কাজে নিয়োগ করতে হবে। তবে, তিনি এও বলেছিলেন, সাবধান থাকতে হবে। কেন না, আমাদের কোনো দুর্বলতার সুযোগে এদের কেউ কেউ যে কোনো সময় পুরনো শ্রেণি স্বার্থবোধের চাপে বিপ্লব এবং সমাজতন্ত্রের সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গ করতে পারে।
পরবর্তী আলোচনায় ঢোকার আগে এখানে জানিয়ে রাখি, উদারনৈতিক রাজনীতির দিক থেকে বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মাক্স হ্বেবারও এক সময় রাষ্ট্রকে “ন্যায়সঙ্গত হিংসার হাতিয়ার” হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁর মতে সমাজে রাষ্ট্রের ন্যায়সঙ্গত আধিপত্য বজায় থাকার ক্ষেত্রে তিন রকম ভাবনার জাল কাজ করে থাকে। এই ব্যাপারে তাঁর মরণোত্তর প্রকাশিত (১৯২২) শেষ (এবং এক ভীমাকৃতি) গ্রন্থে তিনি লিখেছিলেন: “There are three pure types of legitimate domination. The validity of the claims to legitimacy may be based on:
1. Rational grounds — resting on a belief in the legality of enacted 'rules and the right of those elevated to authority under such rules to issue commands (legal authority).
2. Traditional grounds — resting on an established belief in the sanctity of immemorial traditions and the legitimacy of those exercising authority under them (traditional authority); or finally,
3. Charismatic grounds — resting on devotion to the exceptional sanctity, heroism or exemplary character of an individual person, and of the normative patterns or order revealed or ordained by him (charismatic authority) .” [Weber 1978, 215]
এই প্রকার ভেদের জন্য তিনি অবশ্য দেশ কাল ভেদের কথা বা শ্রেণিগত দমন পীড়নের প্রসঙ্গ তোলেননি। তার থেকে মনে হয়, তিনি সমস্ত পর্যায়ের সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় দমন পন্থার সপক্ষে এই ধরনের ভাবনাচিন্তাগুলি কাজ করেছে বলে মনে করতেন। প্রথম ক্ষেত্রটা হচ্ছে যে কোনো রাষ্ট্র যে আইন কানুনের সাহায্যে দমন প্রক্রিয়া চালু রাখে তাকে ন্যায়সঙ্গত বা উচিত বলে মেনে নেওয়া। অবশ্য কারা মানাতে চায় এবং কীভাবে, আর কারা মেনে নেয় এবং কেন — সেই প্রশ্নে তিনি কিছু বলেননি। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এটা সত্যিই যে একবার একটা প্রথা বা ব্যবস্থা চালু হয়ে গেলে একটা সময় থেকে তা ঐতিহ্যিক গুরুত্ব বা তাৎপর্য লাভ করে ফেলে। তখন তাকে মেনে চলতে আর জনসাধারণের কোনো অসুবিধা হয় না। বরং তাকেই স্বাভাবিক বলে মনে হতে থাকে। তিন নম্বর যে কারণটা হ্বেবার দেখিয়েছেন, তা নানা কারণে সামাজিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সমস্ত দেশে কালেই সমস্ত শাসক শ্রেণি জনগণের সামনে — যদি সেরকম সুযোগ আসে — তাদের এক আধজন প্রতিনিধি চরিত্রকে অতিমানব হিসাবে দেখাতে চায়, তুলে ধরতে চায়। যদি সেটা সম্ভব হয়, তাহলে রাষ্ট্রীয় আধিপত্যকে সহনশীল করে তোলা আরও সহজ হয়ে যায়।
মোদ্দা কথাটা হল, শ্রেণির প্রশ্নটা না তুললেও একজন অমার্ক্সবাদী সমাজতাত্ত্বিকের পক্ষেও বাস্তবে সমাজে বিদ্যমান রাষ্ট্রের দমনকারী ভূমিকার কথা তুলে ধরতে হয়েছে। আবার মার্ক্সবাদীদের মতো করে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিবর্তনের বিজ্ঞানী সুলভ বিচার না করার জন্যই তিনি আর এই দমন মূলক যন্ত্রের ঐতিহাসিক ভূমিকা কীভাবে বা সমাজ বিকাশের কোন পর্যায়ে বিলুপ্ত হতে পারে বা হবে — সেই বিষয়ে কোনো আলোচনা পাড়েননি।
[৫]
উপরকাঠামোর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রই হচ্ছে একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেটা শ্রেণি সমাজের প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত চলে এসেছে এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অনেক দিন পরে পর্যন্ত টিকে থাকবে। সারা পৃথিবী জুড়ে অধিকাংশ দেশে সমাজতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর সেই সব দেশের ভেতরে ও বাইরে থেকে বিপরীতমুখী প্রতিবিপ্লবের সম্ভাবনা নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার পরই একমাত্র সেই দেশগুলিতে রাষ্ট্রের অবলুপ্তির প্রক্রিয়া শুরু হবে। আমাদের কালে সমাজতন্ত্র স্থাপিত হলেও খুব স্বাভাবিক কারণেই সাম্যবাদী সমাজে উত্তরণ ও রাষ্ট্রের অবলুপ্তির কোথাও কোনো সূচনা দেখা যায়নি। এবং ধনতান্ত্রিক সমাজে সর্বহারা বিপ্লবের ক্ষেত্রে লেনিনের মতে প্রধান রাজনৈতিক মুদ্দাই হল রাষ্ট্রক্ষমতার প্রশ্ন। এক শ্রেণির হাত থেকে অন্য শ্রেণি হাতে রাষ্ট্রের ক্ষমতার হস্তান্তর। তাই মার্ক্সবাদীদের রাষ্ট্র সম্পর্কে খুব ভালো করে অধ্যয়ন করতে হবে।
যে কোনো রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গ: আইনসভা (legislative body), প্রশাসন যন্ত্র (executive body) এবং বিচার বিভাগ (judiciary)। একটা দেশ কীভাবে চলবে, সেই ব্যাপারে আইনসভা নীতি নিয়ম কর্মসূচি নির্ধারণ করে। প্রশাসন যন্ত্রের কাজ হল সেই নীতি নিয়ম সমূহকে কাজে পরিণত করা। বিচার ব্যবস্থা লক্ষ্য রাখে এই নিয়মকানুন কীভাবে রক্ষিত হচ্ছে। কোথাও তা লঙ্ঘিত হলে অপরাধীকে আইনের আওতায় এনে বিচারের মাধ্যমে শাস্তির বিধান দেওয়া। সরকার এবং প্রশাসনও এই বিচারের আওতায় থাকে। এই অঙ্গগুলি বুর্জোয়া রাষ্ট্র এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যতটা স্পষ্টভাবে সনাক্ত করা যায়, দাস সমাজ বা সামন্ততন্ত্রের ক্ষেত্রে অতটা স্পষ্ট নয়। তথাপি বিষয়টা বুঝে নেওয়া প্রয়োজন।
এই দুরকম সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রেই রাজা বাদশাহ বা সম্রাটই হচ্ছে নীতি নির্ধারক কর্তৃত্ব। আবার তারাই হচ্ছে বিচারক বা শাস্তি প্রদায়ক কর্তৃত্ব। কোতোয়াল ও সেনাবাহিনী হচ্ছে প্রশাসনিক হাতিয়ার। এই দুই বাহিনীর সাহায্যে রাজতন্ত্র সাধারণত যথাক্রমে অভ্যন্তরীন আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করত এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা নিশ্চিত করত। অবশ্য অন্য রাজ্য আক্রমণ করার জন্যও সেনাবাহিনীকে কাজে লাগানো হত। একজন রাজার অধীনে ছোটখাটো জমিদাররাও এক দিকে কাছারিতে লোক নিযুক্ত করত দৈনন্দিন কাজকর্ম হিসাব নিকাশ পরিচালনা করার জন্য। অপর দিকে তাদের হাতেও পাইক বরকন্দাজ লেঠেল বাহিনী থাকত বেয়াদব প্রজাকে ধরে এনে শাস্তি দান এবং অন্যত্র লুটতরাজ মারদাঙ্গা করার উদ্দেশ্যে।
রোমান সাম্রাজ্যে নাগরিক শৃঙ্খলার নামে কিছু আইন কানুন রচিত হয়েছিল। ধারা উপধারা দিয়ে সুনির্দিষ্ট নিয়মের লিখিত বয়ানের সেই নিদর্শন পরবর্তী কালে ইউরোপ ও এশিয়ার অনেক দেশই গ্রহণ করে। ভারতে আবার ধর্মসূত্র বা স্মৃতিশাস্ত্রের নামে একাধিক গ্রন্থ রচিত হয়। এইগুলিতে ধর্মীয় সামাজিক পারিবারিক আচার বিচারের কথাই বেশি করে আছে। গৌতম মনু পরাশর ইত্যাদির নামে এই শাস্ত্রগ্রন্থগুলি প্রচলিত থাকলেও প্রকৃত পক্ষে এগুলোর কোনটা কার লেখা এবং কবে প্রথম রচিত — এখনও খুব নির্দিষ্ট আকারে বলা মুশকিল। চাণক্য বা কৌটিল্যের নামে প্রচলিত অর্থশাস্ত্রও এক রকমের সামাজিক বিধিশাস্ত্র। তবে এতে আবার ধর্মীয় আচার বিচারের কথা প্রায় নেই বললেই চলে।
ইউরোপের বৃহৎ সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি কিছু দূর বিকশিত হওয়ার পর অবশ্য ইতিমধ্যে অন্যত্র গড়ে ওঠা ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার দেখাদেখি রাষ্ট্রযন্ত্রকে আরও খানিকটা পরিশোধিত ও উন্নত আকার দেবার চেষ্টা করে। বিধিবদ্ধ আইন কানুন এবং বিচার ব্যবস্থা গড়ে উঠতে দেখা যায়। রাশিয়ায় এমনকি বিশ শতকের প্রথম দশকে তুমুল গণ বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের পরে জারতন্ত্র শাসন সংস্কারের নামে “দুমা” নামক এক ধরনের দুর্বল সংসদীয় ফোরাম স্থাপন করে এবং তার জন্য নির্বাচনেরও ব্যবস্থা করা হয়। তবে আইন সভা হিসাবে এই মঞ্চের কাজের এক্তিয়ার ছিল খুবই সীমিত।
পশ্চিম এশিয়ায় আরবদের উদ্যোগে এক সময় যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে, সেখানে খলিফা (অর্থাৎ, সর্বোচ্চ শাসক)-ই ছিল একাধারে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কর্তৃত্বের প্রতিভূ। ইসলামিক শাসনেও হাদিশ এবং শরিয়ার মাধ্যমে জনসাধারণের জন্য বেশ কিছু ধর্মীয় ও সামাজিক আচার বিচার নিয়ম নীতি প্রথা ইত্যাদির কাঠামো গড়ে তোলা হয়। সমস্ত মুসলিম দেশই এই নিয়মগুলি কম বেশি মেনে চলে।
একজন সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ দেখিয়েছেন, মধ্য যুগে খ্রিস্টান এবং ইসলামিক ধর্মতন্ত্র এক দিক থেকে সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্রের অংশ ছিল, অপর দিকে এরা নিজেরাও প্রায় এক সমান্তরাল রাষ্ট্রব্যবস্থার মতোই কাজ করত। “Naturally, the Christian Church in Europe and the Moslem organizations in the Eastern countries became an important part of the state apparatus of feudal society.” [Chesnokov 1969, 301] প্রকৃত পক্ষে ক্যাথলিক চার্চ রোমের ভ্যাটিক্যানে একটা সমান্তরাল রাষ্ট্র স্থাপন করে ফেলেছিল, যাদের নিজস্ব বিচার বিভাগ, কয়েদঘর এবং জহ্লাদ বাহিনী ছিল।
[৬]
রাষ্ট্র নির্মাণের প্রশ্নে বুর্জোয়া বিপ্লব কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করেছিল। সেই নতুন বৈশিষ্ট্যগুলি এক এক করে দেখে নেওয়া যাক:
এক, এযাবত কাল দাস প্রথার আমলে এবং সামন্ততন্ত্রে শোষক শ্রেণির সদস্যরা সরাসরি রাষ্ট্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। যে রাজা জমিদার সর্বোচ্চ শাসক, সেইই আবার খাজনা আদায় করে গরিব প্রজাদের থেকে সম্পদ হাতিয়ে নিত। অর্থাৎ, যে শোষক, সেইই শাসকও হত। বুর্জোয়া বিপ্লবের পরে শোষক শ্রেণির সদস্যরা অনেক সময়ই শাসক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে না। তাদের প্রতিনিধিরা শ্রেণিস্বার্থবোধের ভিত্তিতে শাসন চালায়। একটা বুর্জোয়া রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বা প্রধান মন্ত্রী নিজেও যে একজন পুঁজিপতি হবেই — এর কোনো মানে নেই। যদিও হওয়ার ক্ষেত্রেও কোনো বাধা নেই। তবে, যত দিন যাচ্ছে, ধনতন্ত্র একটা শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থা হিসাবে যত প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র অর্জন করছে, ক্ষয়িষ্ণু এবং ধ্বংসোন্মুখ হয়ে উঠছে, ততই পুরনো অনেক আবরণই সে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। আমেরিকায় যেমন রোনাল্ড রেগান, কিংবা জর্জ বুশ, অথবা ডোনাল্ড ট্রাম্প — এরা নির্লজ্জ ভাবেই বিভিন্ন মনোপলি হাউজের মালিক এবং সেই হিসাবে নিজেদের শ্রেণিগত ব্যবসায়িক স্বার্থে সরকারি নীতি প্রণয়ন ও প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যেই রাজনৈতিক ক্ষমতায় ঢুকে আসতে চায়। ভারতেও বর্তমান বিজেপি সরকারের মন্ত্রী এবং এম-পিদের এক বিরাট অংশই নানা সেক্টরের পুঁজি ব্যারন। সব পুঁজিবাদী দেশের অবস্থা কিন্তু এখনও এরকম নয়।
দুই, বুর্জোয়া ব্যবস্থাতেই উপরকাঠামোয় প্রথম রাজনৈতিক দল দেখা দিল। বিভিন্ন শ্রেণির স্বার্থ দেখার জন্য বিভিন্ন দল। এমনকি একই শ্রেণির বিভিন্ন অংশের সীমিত স্বার্থ নিয়ে চলার জন্য আলাদা আলাদা দল। সামন্ততন্ত্রের একেবারে মধ্য ভাগ পর্যন্ত দলের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। এমনকি যখন ইউরোপের অন্যান্য বুর্জোয়া রাষ্ট্রের অনুসরণে উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের গোড়ায় রাশিয়ায় বিভিন্ন শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী একাধিক দল গড়ে উঠেছিল (যাদের প্রায় প্রতিটিই ছিল বে-আইনি গোপন সংগঠন), তখনও জারের কোনো দল ছিল না। সামন্ততান্ত্রিক শোষক শ্রেণির মতাদর্শ প্রচার এবং তার সমর্থনে আম জনতাকে প্রভাবিত ও সংগঠিত করার জন্য ছিল ধর্ম, ধর্মতন্ত্র, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (গির্জা, মসজিদ, মন্দির, সিনাগগ, প্যাগোডা, ইত্যাদি) এবং ধর্ম প্রবর্তক ও প্রচারক পেশাদার গোষ্ঠী (পুরোহিত, পাদ্রি, ইমাম, ভিক্ষু, ইত্যাদি)। কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণির উৎপাদন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শ্রেণি স্বার্থ দেখার জন্য ধর্মীয় সংকীর্ণ গন্ডীবদ্ধ মতবাদ ও আচার প্রকরণ যথেষ্ট ছিল না। সেই কারণে, সামন্ততন্ত্রের শেষ ভাগে দেখা দিল দল, যারা বিভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে নির্দিষ্ট শ্রেণির (বা গোষ্ঠীর) স্বার্থ অনুযায়ী নির্দেশিকা (কর্মসূচি) তৈরি করে, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের কাছে নিজস্ব দাবিদাওয়া জানায় এবং প্রয়োজনে সেই অনুযায়ী আন্দোলন পরিচালনা বা লবি করার মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করে।
তিন, এইভাবে বিভিন্ন দলের মাধ্যমে দাবিদাওয়া উত্থাপনের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই বুর্জোয়া সমাজের উপরকাঠামোয় বহুদলীয় গণতন্ত্র নামক ব্যবস্থাটির জন্ম। আমরা আগেই যে রাষ্ট্রের একটি উপাঙ্গ হিসাবে নীতি নির্ধারক সভা বা আইনসভার উল্লেখ করেছি, সেটা একটা বুর্জোয়া রাষ্ট্রে পার্লামেন্ট বা সংসদ হিসাবে অভিব্যক্ত হয়। এর ফলে প্রকৃত রাষ্ট্র (পুলিশ, মিলিটারি, বিচার বিভাগ) এবং তার মালিকরা (পুঁজিপতি শ্রেণি) লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে যায়। সামনে চলে আসে সরকার (এই বিষয়ে আমরা পরে আরও কিছু কথা উত্থাপন করব)। শুধু সাধারণ জনগণই নয়, অনেক মার্ক্সবাদীও সরকার আর রাষ্ট্রের মধ্যে ফারাক বুঝতে পারে না বা চিহ্নিত করতে সক্ষম হয় না। সংসদে সর্বজনীন ভোটের মাধ্যমে বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হয়। যে দলের সর্বাধিক সংখ্যক প্রতিনিধি জয়ী হয়, তারাই সরকার ও মন্ত্রীসভা গঠন করে। সংসদে আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে আইন বা নীতি নির্ধারিত এবং/অথবা সংশোধিত হয়। সরকারি আয় ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে বার্ষিক বাজেট অনুমোদিত হয়। একটা আদর্শ বুর্জোয়া রাষ্ট্রে সরকার বা শাসক দল কোনো কিছুই সংসদকে এড়িয়ে গিয়ে কার্যকর করে না।
চার, সরকারকেই রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের আসল অঙ্গ মনে করার ফলে এই তথাকথিত বহুদলীয় গণতন্ত্র একটা মোহ বা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। একটা দল সরকারে একটা পর্বে থেকে জনবিরোধী নীতি ও কর্মের কারণে জনপ্রিয়তা হারালে আর একটি দল তার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলে ভালো ভালো প্রতিশ্রুতি দিয়ে জিতে আসতে পারে। তখন সাধারণ মানুষের মনে এরকম ধারণা হয়, তারা চাইলেই শাসক পরিবর্তন করতে পারে। দেশকে সঠিক ও জনমুখী দিশায় সঞ্চালিত করতে নির্ণায়ক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। আমরা খুব অবাক হয়ে দেখি, আজ থেকে ১৭০ বছর আগে কার্ল মার্ক্স লন্ডনে বসে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একটি প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে শাসক ও বিরোধী দলের মধ্যে যে তর্জা হয়েছিল (১৮৫৫), তার প্রকৃত স্বরূপ অত্যন্ত সাবলীল ও নির্মেদ ভাষায় তুলে ধরেছিলেন: “The skill in conducting parliamentary battles consists of course precisely in ensuring that during the fight it is never the office that is hit but always the person holding the office at a given time, and even he only to an extent that will permit him after being brought down as a Minister immediately to come forward as a candidate for the Ministry. The oligarchy does not perpetuate itself by retaining power permanently in the same hand, but by dropping it with one hand in order to catch it again with the other, and so on.” [Marx 2010, 338]
পাঁচ, বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থায় আসল যে রাষ্ট্র — কার্যকর বিভাগ (প্রশাসন, পুলিশ ও সামরিক বাহিনী) এবং বিচার বিভাগ (আদালত ও কারা বিভাগ) — তাদের কাজের ধরন হচ্ছে, উপর থেকে দেখলে মনে হবে, তারা শুধুই হুকুমের চাকর; সরকার যা করতে বলে তারা সেটুকুই করে, সরকারি নীতি অনুযায়ীই তারা চলে, তার বাইরে তারা যেতে পারে না, বা যায় না, ইত্যাদি। অথচ, প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, দেশের জনসাধারণের শুধু মাত্র সংসদের প্রতিনিধি নির্বাচনের ভোটাধিকার থাকে; ক্যাবিনেট সচিব, পুলিশের অধিকর্তা, মিলিটারি জেনারেল, প্রমুখ কেউ নির্বাচিত হন না, নির্বাচনে তাঁদের দাঁড়াতেও হয় না। তাঁরা পরীক্ষা দিয়ে প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হয়ে একবার আসনে বসে গেলে — সরকারে যে বা যারাই আসুক বা যাক — স্থায়ীভাবে নিজ নিজ বিভাগে থেকে যান এবং ধাপে ধাপে প্রোমোশন পেয়ে উপরে উঠে যেতে পারেন। প্রশিক্ষণ এবং কাজের জায়গার বিদ্যমান আবহাওয়ায় তাঁদের মানসিক গঠনে তাঁরা আইন শৃঙ্খলা রক্ষার পক্ষে, অশান্তি ও অরাজকতার বিরুদ্ধে, স্থিতাবস্থা বজায় রেখে চলার স্বার্থে শাসক শ্রেণির অনুকূল অনুভাবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন।
ছয়, এর ফলে এক বিরাট অংশের মানুষের কাছে, এমনকি শিক্ষিত ও মার্ক্সবাদে দীক্ষিত লোকজনের কাছেও, বুর্জোয়া রাষ্ট্রের শ্রেণি চরিত্র আড়ালে থেকে যায়। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সংবিধান, সংবিধানে গৃহীত ব্যক্তি স্বাধীনতা সংক্রান্ত নানা রকম অধিকার, পর্যায়ক্রমিক বহুস্তরীয় ভোট এবং ভোটাধিকার, শাসক দলের পরিবর্তন — ইত্যাদি বুর্জোয়া গণতন্ত্র সম্পর্কে নানা রকম ভ্রান্ত ধারণার জন্ম দেয়। অন্য দিকে বুর্জোয়া শ্রেণির কাছেও এই সমস্ত ঘোষিত সাংবিধানিক অধিকারগুলি অনেক সময়ই শ্রমিক বা কৃষকদের বিরুদ্ধে কোনো নবতর আক্রমণ নামিয়ে আনতে বা জনগণের কোনো গণতান্ত্রিক অধিকার সঙ্কুচিত করতে চাইলে তার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, বা দাঁড়াতে পারে। তাই তাদেরও লক্ষ্য থাকে নানা প্রক্রিয়ায় এই অধিকারগুলিকে কেড়ে নিতে বা নিদেন পক্ষে অকেজো করে রাখতে। এর ফলে জন মানসের অগোচরে সরকারি ব্যবস্থা ও সংসদকে এড়িয়ে নানা রকম বিধিনিষেধ চালু করে ফেলা এখন সমস্ত বুর্জোয়া রাষ্ট্রের একটা চালু প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে। এর থেকে ভুবন জোড়া রাজনীতিতে এসেছে একটা নতুন শব্দ — গুপ্ত রাষ্ট্র (deep state), যা লোকচক্ষুর অন্তরালে দৃশ্যমান রাষ্ট্রের সমান্তরালে ক্রিয়া করতে থাকে। এর মধ্যে আছে দেশি বিদেশি কর্পোরেট সংস্থাগুলির নানা প্রতিনিধি স্থানীয় ফোরাম ও তার সদস্যবৃন্দ, লগ্নিকারক সংস্থাগুলির প্রতিনিধি, আমলাতন্ত্র, পুলিশ এবং মিলিটারির উপরমহলের অদৃশ্য ক্লাব বা অন্য কোনো মিলন ক্ষেত্র, ভিআইপি-দের সঙ্গে সরকারি নেতা মন্ত্রীদের নৈশ ভোজ, কনক্লেভ, জন্মদিনের পার্টি, ইত্যাদি। তাদের সেই সব সমাবেশে দেশের সমাজ অর্থনীতি আইন কানুন পরিবেশ জল জঙ্গল জমি খনি পাহাড় নিয়ে অনেক কিছু লেনদেন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যায়, যার কিছু কিছু অংশ কেবল মাত্র রূপায়ণের সময় আমাদের সামনে পরিদৃশ্যমান হয়। অনেক কিছুই আবার আম জনতার সামনে আসেই না। তারা শুধু ফল ভোগ করে। জার্মানি এবং ইতালিতে ফ্যাসিস্ত শাসন কালে এই জিনিসটা প্রথম শুরু হয়। তার পর বিভিন্ন স্বৈরাচার শাসিত দেশে — তুরস্ক, স্পেন, পর্তুগাল, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, চিলি, ইত্যাদি এই সংস্কৃতি চালান হয়ে যায়। বর্তমানে ভারত বা বাংলাদেশেও এই জাতীয় পরিঘটনা আক্ছার ঘটে চলেছে। তাই রাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনার সময় আমাদের এই দিকটা সম্পর্কেও সচেতন থাকতে হবে।
দু একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।
এই গুপ্ত রাষ্ট্রের ক্রিয়া বোঝা যাবে যদি আমরা ভারতের ক্ষেত্রে বর্তমান বিজেপি সরকারের প্রতিহিংসা পরায়ণ কিছু আচরণ এবং তাতে কীভাবে পুলিশ ও বিচার বিভাগ পৃষ্ঠপোষণ করছে সেটা লক্ষ করি। অশীতিপর সমাজকর্মী ফাদার স্টান স্বামীকে ওরা বিনা বিচারে বন্দি করে যেভাবে জেলে ঢুকিয়ে জেনে শুনে চিকিৎসার বন্দোবস্ত না করে মেরে ফেলল, আদালত যেভাবে এনআইএ-র সুচিকিৎসার গল্পে মোহিত হয়ে গেল, এটা খুবই অদ্ভুত! একই কায়দায় জি এন সাইবাবাকেও ওরা মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে জেলে পচিয়ে মেরে ফেলার আয়োজন করে দিল। দিল্লি পুলিশ কোনো কেস দিতে পারছে না, তথাপি (আরও কয়েকজন সহ) জেএনইউ-র মেধাবী ছাত্র উমর খালিদকে এক মিথায় মামলায় ফাঁসিয়ে পাঁচ বছরেরও বেশি জেলে আটকে রেখেছে, অথচ আদালতও তাকে জামিন দিচ্ছে না (বা, সম্ভবত দিতে সাহস পাচ্ছে না)। ওদিকে দেশের আইনে বলা আছে, জামিন দেওয়াই স্বাভাবিক নীতি (bail is the rule)! পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্য জেল বন্দি রাজনৈতিক ও অন্যান্য আসামীদের প্রাপ্য সুযোগসুবিধা একের পর এক কেড়ে নিচ্ছে সম্পূর্ণ নিঃশব্দে। এমনকি বিনা বিচারে বিচারাধীন বন্দিদের ক্ষেত্রেও কোনো নিয়ম কানুন মানছে না। অর্থাৎ, রাষ্ট্র তার নিজেরই তৈরি আইন মানছে না। রাষ্ট্রের ভেতরে আর একটা রাষ্ট্র তৈরি করে সেই অনুযায়ী এই সব ব্যবস্থা চলছে।
বাংলাদেশের প্রাক্তন শেখ হাসিনা সরকারও যেভাবে দেশের মধ্যে এক সমান্তরাল গোপন জেল ব্যবস্থা (তথাকথিত আয়নাঘর) তৈরি করে রেখেছিল, ২০২৪ সালের জুলাই গণ অভ্যুত্থানের জোরে যার তথ্য প্রকাশ পেয়ে গেল, সেও এই গুপ্ত রাষ্ট্রেরই খেলা। এই সব ঘটনা থেকে বোঝা যায়, বুর্জোয়া শাসকদের পক্ষেও এখন আর তাদের নিজেদের তৈরি নিয়মকানুন মেনে দেশ ও সমাজ পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। নানা ব্যাপারেই তারা বে-আইনি রাস্তায় শাসন করার বিচিত্র পদ্ধতি খুঁজে বের করতে ব্যস্ত।
[৭]
যে কোনো রাষ্ট্রের তিন ধরনের কাজ থাকে: রাজনৈতিক কার্যক্রম, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষাগত সাংস্কৃতিক কর্মসূচি। এর মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টি খুব স্পষ্টভাবেই উপরকাঠামোগত কাজের অংশ। কিন্তু অর্থনৈতিক কাজগুলি মূলত ভিতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকে।
একটু বিশদে যাওয়া যাক।
একটা বুর্জোয়া রাষ্ট্র যখন অভ্যন্তরীন শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করে, বৈদেশিক আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করে কিংবা নিজেই অন্য দেশকে আক্রমণ করে, তখন তার কাজগুলি স্পষ্টই রাজনৈতিক। যে কোনো রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিও একটা প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক আচরণ। যেহেতু রাষ্ট মূলত একটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, এটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। এটাকে শাসক শোষক শ্রেণির রাজনীতি হিসাবেও বলা যেতে পারে। কেন না, প্রতিটা রাষ্ট্র যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে থাকে এবং কার্যকর করতে থাকে, তা সর্বদাই শোষক শ্রেণির পক্ষাবলম্বন করে, কখনই তার তরফে সাধারণত এমন কিছু করা হয় না, যেটা শোষিত মানুষের পক্ষে উপকারী এবং/অথবা সুবিধাজনক। যখন শ্রমিকরা কারখানায় ধর্মঘট করে, রাষ্ট্র তার পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করে রাস্তায় এবং কারখানার গেটে। মালিকরা চাইলেই যাতে মজুরদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের গেট থেকে তাড়িয়ে দেওয়া যায়, কাউকে কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়, ইত্যাদি। এরকম কখনও আজ অবধি কেউ দেখেনি, একটা বুর্জোয়া রাষ্ট্রে কোনো কারখানার মালিক তার প্রতিষ্ঠান লক-আউট বা বন্ধ করে দেওয়ার পরে পুলিশ গিয়ে জোর করে কারখানা খোলাচ্ছে, যাতে শ্রমিকদের কাজ চলে না যায়, তাদের অনাহারে মরতে না হয়। বা শ্রমিক ছাঁটাই করলে সেই মালিককে গ্রেপ্তার করেছে। এই পক্ষ নির্বাচন একেবারে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। ২০২৩ সাল থেকে প্রায় সমস্ত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ইজরায়েলের বর্তমান চলমান প্যালেস্তাইন ধ্বংসকারী আগ্রাসনের পাশে দাঁড়িয়েছে, তাকে সমর্থন করে চলেছে, জাতিসঙ্ঘে নিন্দা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে — শুধু আমেরিকা নয়, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইত্যাদি। আর অন্য দিকে যখন প্যালেস্তাইনের সমর্থনে, গাজায় গণহত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষের মিছিলের ঢল নেমেছে, পুলিশ এবং আধা সামরিক বাহিনী দিয়ে তাকে আটকানোর চেষ্টা চালিয়েছে।
এক্ষেত্রে দুরকম ব্যতিক্রম দেখা যায়।
একটা হল, রাষ্ট্রের প্রয়োজনে এক আধজন উচ্ছৃঙ্খল পুঁজিপতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে, বা এমনকি জেলে পাঠাতেও পারে একটা বুর্জোয়া রাষ্ট্র। এটা হল পুঁজিবাদের বৃহত্তর স্বার্থে, পুঁজিবাদকে বাঁচাতেই মালিক শ্রেণির দুএকজন সদস্যকে অন্যায় করলে আইনের নামে শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারে। যদিও এটা হচ্ছে অত্যন্ত দুর্লভ ঘটনা।
আর একটা ক্ষেত্র হচ্ছে, যেখানে একটা ভয়ঙ্কর জনবিরোধী রাষ্ট্র তার নিজের বুর্জোয়া জাতীয় স্বার্থে এমন কোনো একটা সিদ্ধান্ত নেয়, যা হয়ত তাৎক্ষণিক ভাবে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে। যেমন, ভারত সরকার ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাড়তি শুল্ক চাপানোর সামনে মাথা নীচু না করে এখন চিনের সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে। এর ফলে হয়ত কিছু চিনা পণ্য ভারতে আসতে পারবে, যেগুলো স্বাভাবিক বাজার দামের তুলনায় একটু সস্তা হবে।
অর্থনীতির ক্ষেত্রে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের প্রধান ভূমিকা হচ্ছে এক দিকে নানা বিধিসম্মত উপায়ে রাজস্ব সংগ্রহ করা এবং অপরদিকে বিভিন্ন প্রশাসনিক খাতে ব্যয় নির্বাহ করা। যেমন একটা বুর্জোয়া রাষ্ট্র তার নাগরিকদের থেকে সরাসরি আয়কর এবং ব্যবসায়ীদের থেকে বিক্রয় কর সংগ্রহ করে। এই দুটো হচ্ছে যে কোনো দেশের রাষ্ট্রের পক্ষে দুটি প্রধান আয়ের উৎস। এছাড়া বৈদেশিক বাণিজ্য শুল্ক, বিশেষ করে রপ্তানি শুল্ক থেকেও বাণিজ্যিক আয়তনের অনুপাতে রাষ্ট্রের আয় হয়ে থাকে। বিপরীপ দিকে, সরকারি কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা, সংসদীয় প্রতিনিধিদের বেতন ও ভাতা, উভয় ক্ষেত্রে পেনসন, নানা রকম নির্মাণ ও মেরামতি কার্যের ব্যয়, নিরাপত্তা সরঞ্জাম ক্রয় — ইত্যাদিও রাষ্ট্রের ব্যয়ের অন্তর্গত। এছাড়া, দেশের অর্থ বাজার ও মুদ্রাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করাও সরকারের একটা জরুরি কাজ।
পুঁজিবাদ একচেটিয়া পর্বে উন্নীত হওয়ার পর রাষ্ট্রের সঙ্গে একচেটিয়া মালিকদের ক্রমশ একটা অশুভ আঁতাত গড়ে উঠেছে সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশে বিগত দেড়শ বছর ধরে। রাষ্ট্র কর্পোরেটদের নানা অছিলায় আয়করে বিপুল ছাড় দিয়ে থাকে। অস্ত্রশস্ত্র সহ বিভিন্ন ভারি শিল্প পণ্য তাদের কাছ থেকে কেনে বেশি দাম দিয়ে। আর যখন সরকারি দ্রব্য বা পরিষেবা ওদের কাছে বিক্রি করে, সেখানে বহু বিধ ছাড় দেয়, এমনকি প্রায় বিনা মূল্যেও দিয়ে দেয়। ভারতে বিজেপি-র জমানায় যা ঘটছে (যেমন, এখানে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলো থেকে কর্পোরেট সেক্টর লক্ষ কোটি টাকার অঙ্কে ঋণ নিয়ে তা ফেরত দিচ্ছে না এবং সরকার সেই ঋণ মকুব করে দিচ্ছে), এগুলো অবশ্য মাত্রার দিক থেকে অনেকটাই ব্যতিক্রমী ঘটনা, তবে সারা বিশ্ব জুড়েই এই জাতীয় ঘটনা দেখতে পাওয়া যাবে।
১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর দেশে দেশে সমাজতন্ত্র যখন খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠল, এবং বিশেষ করে, ১৯২৯-৩৩ বছরগুলিতে সারা পৃথিবী জুড়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় গভীর সঙ্কটের পর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে প্রায় সমস্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু জনকল্যাণমূলক অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই সব ছিল পুঁজিবাদী শোষণ জর্জরিত শ্রমিক চাষি তথা সাধারণ মানুষকে কিছুটা রিলিফ দেওয়া। তার পর থেকে বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি নিজেদের “জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র” (welfare state) হিসাবে দাবি করতে থাকে। পাঠ্যপুস্তক ও সংবাদ মাধ্যমের সুবাদে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের শ্রেণি চরিত্র অসচেতন জনগণের কাছে আড়াল করার চেষ্টা চলতে থাকে। বহু মানুষ এই প্রচারের দ্বারা খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে থাকেন।
এই সমস্ত রিলিফ দেবার আসল উদ্দেশ্য কী বিবেচনায় নিলেই তথাকথিত কল্যাণের পশ্চাদ রহস্য ধরা পড়ে যাবে। ক্রমবর্ধমান শোষণের ফলে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের লাগাতার মূল্যবৃদ্ধির সাপেক্ষে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যেতে থাকে। তখন কিছু ত্রাণমূলক কর্মসূচির নাম করে নিম্ন আয়ের মানুষের হাতে যেমন যেমন টাকাপয়সা যোগান দেওয়া যায় সেই অনুপাতে বাজারে কেনাকাটা বাড়ে। একজন সোভিয়েত আমলের বিশ্লেষক যথার্থভাবেই দেখিয়েছিলেন: “In actual fact, however, the increasing role played by the bourgeois state in the economy of modern capitalist countries does not signify that this state is turning into a “people’s”, “supra class” state which displays equal concern for the interests of social groups, but manifests the inability of the monopolies to secure extended reproduction of capital without the direct participation of the machinery of state. As things stand, the modern imperialist state controls and regulates economy in the interests of the monopolies, thus giving them the opportunity to turn to their advantage not only their own capital, but also to use the state treasury which is replenished by taxes levied on the population as a sort of machine for pumping out superprofits.” [Selezniyov 1968, 168]
শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও আধুনিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রের একটা বড় ভূমিকা আছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল স্তরের শিক্ষা প্রায় সমস্ত দেশেই মূলত সরকারি তহবিল থেকে পরিচালিত হয়। যদিও বিভিন্ন খ্রিস্টীয় ও অন্যান্য ধর্মীয় মিশনারি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগেও বহু স্কুল কলেজ পরিচালিত হয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় সহ সমস্ত স্তরের শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি বেসরকারি দুরকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকলেও সমস্ত প্রতিষ্ঠানকেই সরকার নির্ধারিত পাঠক্রম ও পরীক্ষা নীতি মেনে চলতে হয়। এসব জায়গায় যারা চাকরি করে তাদেরও প্রতিষ্ঠানের নিয়ম শৃঙ্খলা ছাড়াও রাষ্ট্রীয় নীতি সমূহ পালন করতে হয়। এই যাবতীয় ক্ষেত্রে বুর্জোয়া রাষ্ট্র শাসক বুর্জোয়া শ্রেণির ইচ্ছা অনিচ্ছা পছন্দ অপছন্দকে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। আমাদের দেশের ক্ষেত্রে এটা যতটা স্পষ্ট দেখা যায়, ইংল্যান্ড বা ফ্রান্সের ক্ষেত্রে হয়ত ততটা পরিষ্কার নয়। তবুও গভীরে ঢুকে বিশ্লেষণ করলে এটা ভালো ভাবেই বুঝতে পারা যাবে। মার্ক্স এঙ্গেল্সদের সেই কথাটা এই জায়গায় আজও অত্যন্ত সঠিক ভাবে প্রযোজ্য: “The class which has the means of material production at its disposal, consequently also controls the means of mental production, so that the ideas of those who lack the means of mental production are on the whole subject to it. The ruling ideas are nothing more than the ideal expression of the dominant material relations, the dominant material relations grasped as ideas; . . .” [Marx and Engels 1976, 67]
শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে এই শ্রেণি চিন্তাগত প্রভাব সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়েছে। মূল ধারার সাহিত্য নাটক সিনেমা ইত্যাদিতেও বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে বুর্জোয়া শ্রেণির মদতপুষ্ট ভাবধারার প্রভাব সচেতন কোনো পর্যবেক্ষকের চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না। পক্ষান্তরে, এর বিপরীত চিন্তাধারা নিয়ে যে নাটক সিনেমা সাহিত্য মাথা তুলতে চায়, তাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অসংখ্য বাধাবিঘ্ন মোকাবিলা করে এগোতে হয়। আর যদি বা কিছুটা তৈরি হয়ও, প্রচারের নৈঃশব্দ তাকে অনেকটা লোকচক্ষুর আড়ালে রেখে দিতে সক্ষম হয়।
প্রচারের প্রসঙ্গে বলা দরকার, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রচারের যেটা প্রধান উপকরণ — বড় গণমাধ্যম: মুদ্রিত সংবাদপত্র, রেডিও, দূরদর্শন, ও অন্যান্য — তার সমস্তই আছে বা থাকে বৃহৎ বুর্জোয়াদেরই দখলে, সরাসরি মালিকানায় এবং/অথবা নানা রকম নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাধীনে। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রথম যুগে সংবাদপত্রকে বলা হত গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। অর্থাৎ, উপরে আমরা বুর্জোয়া রাষ্ট্রের যে তিনটি অঙ্গের কথা বলেছিলাম, তার সঙ্গে মিলিয়ে একেও ধরে নেওয়া হয়েছিল, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। কিন্তু রাষ্ট্রের অন্যান্য অঙ্গগুলি যেমন বুর্জোয়া শ্রেণি স্বার্থের পরিপোষণ করে, সংবাদ মাধ্যমও একই কাজ করে চলেছে। যত দিন যাচ্ছে, অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যম — মুদ্রিত বা বৈদ্যুতীন — নিরপেক্ষতার সমস্ত মুখোশ খুলে ফেলে ধীরে ধীরে কর্পোরেট স্বার্থের নির্লজ্জ উপাসকে পরিণত হয়েছে। বর্তমান ভারতবর্ষে সমস্ত বৃহৎ সংবাদ মাধ্যমের উপস্থাপিত সংবাদ বৈচিত্র্য (আসলে সংবাদ একঘেয়েমি) দুচার দিন পর্যবেক্ষণ করলে এটা বুঝতে আর কোনো অসুবিধা হবে না।
মনে রাখতে হবে, মধ্য যুগে ধর্মতন্ত্র যেভাবে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সপক্ষে মতবাদিক প্রচার করে দীর্ঘমেয়াদি জনমত গঠন করে দিত, আধুনিক বুর্জোয়াতন্ত্রের যুগে বৃহৎ গণমাধ্যমও সেই একই ভূমিকা পালন করে শাসক পুঁজিপতি শ্রেণীর পক্ষে জনমনকে প্রভাবিত করতে। মধ্য যুগে ধর্মীয় সংগঠনের প্রচার যতটা স্থূল ও নগ্ন ছিল, পুঁজিবাদের গোড়ার যুগে গণমাধ্যম তার তুলনায় কিছুটা অন্তত নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে অভ্যস্ত হয়েছিল। রাষ্ট্রবিরোধী ভূমিকা না নিলেও এক এক সময়ে বিদ্যমান সরকারের সমালোচনায় অনেকটাই অগ্রসর হত। কিন্তু একচেটিয়া পুঁজিবাদ যত সংহত হচ্ছে, তার কর্পোরেট চরিত্র যতই পরিস্ফূট হচ্ছে, আর অন্য দিকে পুঁজিবাদী অর্থনীতি যত বাজার সঙ্কট, মন্দা, অধোগতি ও পরস্পর বাণিজ্য যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছে, এবং শ্রমিক কৃষক ও শোষিত জনগণের বিপ্লবী গণসংগ্রাম ফেটে পড়ার সম্ভাবনা যত বেড়ে চলেছে, ততই সংবাদ মাধ্যমগুলি একেবারে সামন্তযুগের চার্চের মতোই নিরপেক্ষতার আলখাল্লা খুলে ফেলে মালিক শ্রেণি ও তাদের দালালদের হয়ে কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতে আপ্লুত হয়ে উঠছে।
আর এর সঙ্গে বেড়ে চলেছে মিথ্যা সংবাদ সৃষ্টি ও প্রচার। কোনো একটা উৎস থেকে একবার একটা ভুয়ো খবর রান্না হয়ে কোনো মাধ্যমে জায়গা পাওয়ার পর অন্যান্য গণমাধ্যমগুলি ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে দিনেরাতে লাগাতার প্রচার করে করে প্রায় “সত্য” হিসাবে দাঁড় করিয়ে ফেলতে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় সর্বাধুনিক ইলেকট্রনিক বিদ্যা ও প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে নির্মিত নানা রকম ফেক ছবি ও ভিডিও, যা সেই ভুয়ো খবরকে অসচেতন চোখ ও কানের জন্য আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে থাকে। মুদ্রিত পত্রিকায় তবু আইন বাঁচাতে লেখা হয় — “এই ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করা হয়নি/যায়নি।” টিভি চ্যানেলের সেই দায়িত্বও নিতে হয় না। যদিও যাদের একটা ছবি বা ভিডিওর সত্যতা যাচাই করে নিঃসন্দেহ হয়ে তবেই সাধারণ পাঠকদের কাছে পরিবেশন করার কথা, তারা প্রচারের আগে সেই কাজ করে নেয় না কেন — এটাও ভেবে দেখা দরকার। এই ব্যাপারটা কোনো বিশেষ দেশের বা বিশেষ কাগজ/চ্যানেলের চরিত্র নয়, এটাই এখন গোটা বুর্জোয়া বিশ্বের সমস্ত গণ মাধ্যমের সাধারণ চরিত্র। ব্যতিক্রম প্রায় নেই বললেই চলে।
[৮]
উপরের এই সমস্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমাদের একটা জিনিস অবশ্যই বুঝতে হবে। সেটা হল, সরকার আর রাষ্ট্র এক নয়, সরকারের পরিবর্তন মানেই রাষ্ট্রের পরিবর্তন নয়। একটা কমিউনিস্ট পার্টি প্রতি দিন শ্রমিক শ্রেণি ও অন্যান্য মেহনতি জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনা করে, তার সবই একটা বুর্জোয়া রাষ্ট্রের অন্তর্গত সরকারের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়। সেগুলির লক্ষ্য কখনই রাষ্ট্রের পরিবর্তন সাধন নয়। আবার নির্বাচনের মধ্য দিয়েও যে পরিবর্তন আনা যায় বা আসে, তাও সরকারের পরিবর্তন, রাষ্ট্রের তাতে সামান্যও অদল বদল হয় না। যদিও একথা ঠিক যে শাসক দলের পরিবর্তন হলে সরকারি নীতিতে সামান্য হলেও তফাত থাকতে পারে, এবং সেইটুকু অর্থে, পুঁজিপতিদের স্বার্থ কখনও বেশি কখনও বা কম হলেও আঘাত প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব। কিন্তু সেটাও একটা সীমার মধ্যেই থাকে। সীমা ছাড়িয়ে যায় না।
মার্ক্স এঙ্গেল্স থেকে শুরু করে লেনিন হয়ে রুশ বিপ্লব এবং সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের নির্মাণ কালে এই বিষয়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনের মূল ধারায় কোনো সমস্যা বা বিতর্ক ছিল না। উনিশ শতকের শেষে বিশেষত এঙ্গেল্সের মৃত্যুর পরে এডুয়ার্ড বার্নস্টাইন, কনরাড স্মিট, আর্ল ব্রাউডার, প্রমুখ এবং বিংশ শতাব্দের প্রথম ভাগে কার্ল কাউটস্কি প্রমুখ যে বিভ্রান্তিকর প্রচার চালাতে থাকে, লেনিন সাধ্য মতো তার প্রায় সমস্ত প্রশ্নেরই মীমাংসা করে দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের কথা, স্তালিনের মৃত্যুর পরে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিশতম কংগ্রেসে নিকিতা খ্রুশ্চভ যে রাজনৈতিক রিপোর্ট পেশ করে তাতে আবার এই প্রশ্নে পুরনো বিভ্রান্তিগুলিকে পুনরুত্থাপন করে দেয়। তাতে দাবি করা হয়, বর্তমান (১৯৫০-এর দশকে) বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অভ্যুত্থানের ফলে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির সম্মিলিত শক্তির এতটাই হ্রাস হয়েছে যে ভোটে দাঁড়িয়ে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের মধ্য দিয়েই একটা দেশের কমিউনিস্ট পার্টি স্রেফ সরকার গঠন করে বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে পালটে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারে: “At the same time the present situation offers the working class in a number of capitalist countries a real opportunity to unite the overwhelming majority of the people under its leadership and to secure the transfer of the basic means of production into the hands of the people. The right-wing bourgeois parties and their governments are suffering bankruptcy with increasing frequency. In these circumstances the working class, by rallying around itself the working peasantry, the intelligentsia, all patriotic forces, and resolutely repulsing the opportunist elements who are incapable of giving up the policy of compromise with the capitalists and landlords, is in a position to defeat the reactionary forces opposed to the interests of the people, to capture a stable majority in parliament, and transform the latter from an organ of bourgeois democracy into a genuine instrument of the people's will. In such an event this institution, traditional in many highly developed capitalist countries, may become an organ of genuine democracy — democracy for the working people.” [Khrushchev 1956, 30; emphasis added]
এমন একটা সংশোধনবাদী থিসিস আসার সঙ্গে সঙ্গেই গোটা বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির নেতা পালমিরো তোলিয়াত্তি তত্ত্বগতভাবে এই থিসিস বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে দেবার দায়িত্ব পালন করেন। এই সরকার-বদলে-বিপ্লব সংক্রান্ত রাজনৈতিক লাইন গ্রহণ করে দেশে দেশে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি বুর্জোয়া রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শক্তি সংহত করে বিপ্লবী আন্দোলনের চূড়ান্ত বোঝাপড়ার মানসিক, মতাদর্শিক ও সাংগঠনিক প্রস্তুতি হারিয়ে ফেলতে থাকে। এই বিভ্রান্তির হাত থেকে মার্ক্সবাদীদের সকলে এখনও মুক্ত হয়েছে বলে মনে হয় না।
অথচ, এই বিষয়টাকে পরিষ্কার করার জন্যই সেই ১৮৪৮ সালেই মার্ক্স এবং এঙ্গেল্স কমিউনিস্ট ইস্তাহারে স্পষ্ট করে বলেছিলেন, “The executive of the modern State is but a committee for managing the common affairs of the whole bourgeoisie.” [Marx and Engels 1977, 38] এবং “Political power, properly so called, is merely the organised power of one class for oppressing another.” [Ibid 59] এই রাজনৈতিক ক্ষমতা মানে শুধু সরকার নয়, আরও অনেক কিছু নিয়ে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। এটা ভোটের দ্বারা পালটানো যায় না।
১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের মুখে দাঁড়িয়ে লেনিন আবার মার্ক্স ও এঙ্গেল্সের বক্তব্যকে অনুসরণ করে দেখান: “Because the state arose from the need to hold class antagonisms in check, but because it arose, at the same time, in the midst of the conflict of these classes, it is, as a rule, the state of the most powerful, economically dominant class, which, through the medium of the state, becomes also the politically dominant class, and thus acquires new means of holding down and exploiting the oppressed class. . . .” The ancient and feudal states were organs for the exploitation of the slaves and serfs; likewise, “the modern representative state is an instrument of exploitation of wage-labour by capital. By way of exception, however, periods occur in which the warring classes balance each other so nearly that the state power as ostensible mediator acquires, for the moment, a certain degree of independence of both. . . .” Such were the absolute monarchies of the seventeenth and eighteenth centuries, the Bonapartism of the First and Second Empires in France, and the Bismarck regime in Germany. [Lenin 1974, 397]
আবার, “The state is a product and a manifestation of the irreconcilability of class antagonisms. The state arises where, when and insofar as class antagonism objectively cannot be reconciled. And, conversely, the existence of the state proves that the class antagonisms are irreconcilable.” [Ibid, 392]
এই জন্যই এক শ্রেণির রাষ্ট্রের দ্বারা অন্য শ্রেণি স্বার্থ রক্ষিত হতে পারে না: “According to Marx, the state is an organ of class rule, an organ for the oppression of one class by another; it is the creation of “order”, which legalises and perpetuates this oppression by moderating the conflict between the classes.” [Ibid]
তাই শেষ পর্যন্ত শোষণ মুক্তির জন্য সর্বহারা শ্রেণিকে সশস্ত্র বিপ্লবের আঘাতে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভেঙে ফেলে তার বদলে নতুন করে শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্র (সর্বহারার একনায়কত্ব) প্রতিষ্ঠা করতে হবে: “If the state is the product of the irreconcilability of class antagonisms, if it is a power standing above society and “alienating itself more and more from it”, it is clear that the liberation of the oppressed class is impossible not only without a violent revolution, but also without the destruction of the apparatus of state power which was created by the ruling class and which is the embodiment of this “alienation”.” [Ibid 393; emphasis added]
যদিও একথার মানে এরকম বুঝলে ভুল হবে যে বুর্জোয়া ব্যবস্থায় একটা কমিউনিস্ট পার্টি বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিত্বমূলক সভার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে না, কিংবা, ভোটে জিতে একা বা অন্যান্য কাছাকাছি দলের সঙ্গে জোট বেঁধে বোর্ড তথা সরকার গঠন করতে চেষ্টা চালাবে না। রাজনৈতিক ভাবে মোহ মুক্ত হয়ে গণ আন্দোলনের কার্যক্রম চালাতে চালাতে নির্বাচনেও দাঁড়াতে হবে, জয়ের চেষ্টা করতে হবে, যেখানে যে স্তরে যতটকু সুযোগ আসবে তাকে ব্যবহার করে সরকারি ক্ষমতায়ও যেতে এবং নানা রকম প্রগতিশীল সামাজিক অর্থনৈতিক সংস্কারের চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই খ্রুশ্চভীয় থিসিস মেনে মনের মধ্যে বা প্রকাশ্যে সংসদীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে কোনো মোহ তৈরি করে রাখা উচিত হবে না। বরং নিরন্তর প্রচার সংগঠিত করা এবং উপযুক্ত কর্মসূচি গ্রহণের মধ্য দিয়ে সেই মোহ কাটানোই হবে কমিউনিস্টদের প্রধান লক্ষ্য। এভাবে না বুঝলে রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্ক্সীয় প্রেক্ষিত থেকে আলোচনা অর্থহীন বাগাড়ম্বরে পর্যবসিত হবে।
গ্রন্থসূত্র:
D. I. Chesnokov (1969), Historical Materialism; Progress Publishers, Moscow.
Frederick Engels (1968), The Origin of the Family, Private Property and State; Progress Publishers,
Moscow.
Cris Harman (1994), “Engels and the Origin of Human Society”; International Socialism, Vol. 2, Issue 65
(Winter 1994).
Nikita Khrushchev (1956), Report of the Central Committee to the 20th Congress of the Communist
Party of Soviet Union (Bolshevik); Progress Publishers, Moscow. February 14, 1956.
V. I. Lenin (1974), State and Revolution; Collected Works, Vol. 25; Progress Publishers, Moscow.
Karl Marx (2010), “From Parliament. — Roebuck’s and Bulwer’s Motions”; Karl Marx and Frederick
Engels (2010), Collected Works, Vol. 14; Lawrence and Wishart, London (digital edition).
Karl Marx and Frederick Engels (1976), The German Ideology; Progress Publishers, Moscow.
Karl Marx and Frederick Engels (1977), Manifesto of the Communist Party; Progress Publishers,
Moscow.
William Paul (2012), The State: Its origin and function ; Phoneme Publisher, New Delhi.
D. I. Selezniyov (1968), “Problems of the State”, G. Glezerman and G. Kursanov (ed. 1968), Historical Materialism: Basic problems; Progress Publishers, Moscow.
Max Weber (1978), Economy and Society: An outline of interpretive sociology; University of California Press, Los Angeles.

 By :
By :